
মুখবন্ধ
দেশভাগের বিভীষিকাময় দিনগুলোর কথা নারী ও পুরুষের জবানবন্দিতে ভিন্নভাবে ধরা দেয় কেন? জন্মভূমির পিছুটানে আবার ঘরে ফেরা নাকি হারানো বাস্তুভিটের স্মৃতিচারণ,উদ্বাস্তুরা কোনটায় বেশি স্বচ্ছন্দ? তাঁর চতুর্থ তথ্যচিত্রের পঞ্চম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে দেশভাগের ঘূর্ণিপাকে পড়ে যাওয়া মানুষদের চোখের জলের নেপথ্যকাহিনীকে ঘিরে তৈরি তথ্যচিত্র দেখার গুরুত্বের কথা জানালেন বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক সুপ্রিয় সেন।
বিএফএ এই কাজটার দায়িত্ব নিল কেন:
দেশভাগকে কেন্দ্র করে বানানো মূলধারার সিনেমা নিয়ে আলোচনা হলে তা প্রায় আগাগোড়াই আবর্তিত হয় ঋত্বিক ঘটকের মেঘে ঢাকা তারা (১৯৬০), কোমল গান্ধার (১৯৬১), সুবর্ণরেখা (১৯৬২) -এই ফিল্মগুলি ঘিরে। কখনোসখনো অবশ্য নিমাই ঘোষের ছিন্নমূল (১৯৫০), রাজেন তরফদারের পালঙ্ক (১৯৭৫), গৌতম ঘোষের শঙ্খচিল (২০১৬), সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের রাজকাহিনী (২০১৫) এবং লীনা গঙ্গোপাধ্যায় আর শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাটি (২০১৮) এগুলির নামও উঠে আসে। কিন্তু যতটা গভীরে গিয়ে এই বিষয় নিয়ে তথ্যচিত্র মাধ্যমে কাজ করা হয়েছে সেই নিয়ে তথ্যচিত্র নির্মাতা ও তাদের সহায়করা ছাড়া কেউই বিশেষ কথা বলেন না। এই অকারণ অনাগ্রহ সত্যিই বিস্মিত ও ব্যথিত করে।সুপ্রিয় সেন দেশভাগের সময়কার উদ্বাস্তুদের জীবনকাহিনী ফুটিয়ে তুলতে অনেক পরিশ্রম করেছেন। তিনি এই কারণে অনেকটা ঝুঁকিও নিয়েছেন। ভালোবাসা, হারানোর যন্ত্রণা এবং ফিরে পাওয়ার ইচ্ছেরা তার নেওয়া ইন্টারভিউতে আপনিই ধরা দিয়েছে। তাই, স্বাধীনতার ৭৬ বছর পূর্তিতে, সীমান্তের ইতিহাসের খাতাটি তাকে ছাড়া খুলে দেখা অসম্ভব!
স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক হিংসার বলি হয়ে লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু হয়, প্রায় ৭৫,০০০ নারী অপহৃতা, ধর্ষিতা হন। সব মিলিয়ে প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ বাস্তুহারা সেই সময় হাজার, হাজার পরিবার পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিলেন। তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। বহু গ্রাম খালি করে বাসিন্দারা পালিয়ে গেছে। রিফিউজি ক্যাম্পে ঠাই হয়েছিল লক্ষ, লক্ষ মানুষের। কিন্তু সহায় সম্পদহীন উদ্বাস্তু মানুষের জীবন যন্ত্রণা এখানেই শেষ হয়নি পরবর্তীকালে, দশকের পর দশক জুড়ে রিফিউজি ক্যাম্পে বা তার বাইরের নির্মম জীবনসংগ্রামে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসের এটাই ছিল সবচেয়ে বড় স্থানান্তরণ!
অথচ এদেশের ইতিহাসের চর্চায় স্বাধীনতার কথা বড় বড় করে লেখা হলেও দেশভাগ আর উদ্বাস্তুদের কথা খালি ফুটনোট হয়ে থেকে গেছে। কিন্তু আমার ব্যাক্তিগত পরিসরটা ছিল এর ঠিক বিপরীত। আমার মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীরা সকলেই ছিলেন উদ্বাস্তু মানুষ। ১৯৪৭ এর দেশ ভাগের পর এরা সকলেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতবর্ষে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে আসার যন্ত্রণা আজীবন তাঁদের মনের গভীরে এমন ভাবে প্রোথিত ছিল যে নিজেদের মধ্যে একত্রিত হলেই তারা অনর্গল “ফেলে আসা দেশ, ছেড়ে আসা গ্রাম” এর গল্প করতেন । আমার ছোটবেলায় দেশভাগের সেইসব মর্মস্পর্শী কাহিনী গুলো ছিল রূপকথার গল্পের মতো, যা আমার প্রাপ্তবয়স্ক সত্তা তার সচেতন ও অবচেতনকে গঠন করে দেয়। এদেশের অতীত, বর্তামান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক অমীমাংসিত প্রশ্নের জন্ম দেয় আমার মধ্যে। এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই আমি দেশভাগ নিয়ে ছবি করা শুরু করি।

এর আগে ব্যক্তিগত পরিসরে গল্প শোনার বাইরে গিয়ে আমি যখন এই বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতে শুরু করলাম তখন উর্বশী বুটালিয়া, নিশিদ হাজারি ইত্যাদিদের বই থেকে দেশভাগের সময়কার নৃশংসতার বিভিন্ন আখ্যান জানতে পারি। অবাক লাগে এটা জেনে যে নাতসি ডেথ ক্যাম্পের অমানবিক অত্যাচার চাক্ষুষ করেছেন এমন অনেক ব্রিটিশ সৈনিক এবং সাংবাদিকরাও বলেছেন দেশভাগের সময়কার পাশবিকতা নাকি ছিল আরো ভয়ঙ্কর। আমি যত বেশি পড়ছিলাম, ততই আরো বেশি প্রশ্ন আমার মাথায় ভিড় করছিল। বহু ধর্মাবলম্বী মানুষদের নিয়ে তৈরি কোন সমাজে ভাঙন ধরলে ঠিক কী ঘটে সেটা আমি গভীর ভাবে জানতে চেয়েছিলাম। মানব ইতিহাস অনুযায়ী সর্বাধিক মানুষের বাধ্যতামূলক দেশত্যাগের ঘটনার প্রভাব এই উপমহাদেশের নাগরিকদের মানসিকতার ওপর কতটা সুদূরপ্রসারী সেটাও বোঝার চেষ্টা করেছিলাম। সবশেষে, আমার প্রশ্ন ছিল ১৯৪৭ সালে ঘৃণার বিষবৃক্ষ রোপণ করা হয়, তার শিকড় কি আরো গভীরে প্রোথিত হয়েছে? নাকি ভাঙ্গনের পর আমরা সহ নাগরিক বা প্রতিবেশী হিসেবে বাঁচতে শিখেছি? ইতিহাসের দিকে যদি আজ আমরা আবার ফিরে তাকাই তবে তার থেকে কি শিক্ষা নেব, চিরস্থায়ী দ্বন্দ্বের না শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের?
আমি জানতাম খালি বইয়ের পাতাতেই এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে না। শুধুমাত্র স্মৃতিকথা আর গবেষণাপত্রে সব সত্য লুকিয়ে নেই। বুঝতে পেরেছিলাম যে উত্তরগুলো খুঁজে পেতে হলে আমায়, আমার মা-বাবার ফেলে আসা গ্রামে যেতেই হবে। এ ভাবেই ২০০০ সালে বাবা মাকে নিয়ে তাঁদের দেশ বরিশালে ফিরে গেলাম, যেখান থেকে পঞ্চাশ বছর আগে প্রাণ হাতে করে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে এসেছিলেন তাঁরা। এই তথ্যচিত্রগুলো বানানোর সময় অনেকেই আমায় বলেন যে স্মৃতিগুলো নিয়ে জীবন কাটলে কাটুক না!
অনেকে এমনটাও বলেন যে উদ্বাস্তুদের জবানবন্দির কোন ভরসা নেই কারণ সেগুলো হল এক সোনার দেশের কষ্টকল্পনা মাত্র। সেই কাল্পনিক সোনার দেশ হয়ত কোনদিন ছিলই না, আর থাকলেও তার বাস্তব রূপটি কল্পনার থেকে সম্ভবত একেবারেই আলাদা। তার চেয়ে স্মৃতিই ঢের ভাল। অতীতের সাথে আপোস করে নেওয়ার পরামর্শ দেন অনেকেই। যে অকল্পনীয় মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে তারা গেছেন সেটা তাদের আর ঘুরে তাকানোর অনুমতি হয়ত দেয়না। বাস্তবে, স্মৃতি কিন্তু সততই সুখের হয় না। যেমন, জন্মস্থলে ফেরার খুব একটা আগ্রহ আমার বাবার মধ্যেও আমি দেখিনি। কিন্তু আমি নিজে বিশ্বাস করতাম অতীতের সঙ্গে সম্যক বাক্যালাপ দরকার। আমার তৈরি পাঁচটা তথ্যচিত্রই আসলে অতীতের সাথে একটা বোঝাপড়ার সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস। আমার বাবা কিন্তু বরিশালে পা রাখার পর খুব খুশি হয়েছিলেন। আর আমার মনে হয়েছিল যে মায়ের কাছে শোনা বাংলাদেশের গল্পের চেয়েও সেই দেশ যেন আরো বেশি সুন্দর।
তার পর দুই দশক
কেটে গেছে, কিন্তু দেশভাগ নিয়ে আমার আগ্রহে একটুও ঘাটতি পড়েনি। এর মাঝেই দেশভাগ নিয়ে
বানিয়ে ফেলেছি পাঁচটি
তথ্যচিত্র!
পূর্ব
পাকিস্তান
থেকে
ভারতে
চলে
আসা
উদ্বাস্তুদের
জীবন
ঘিরে
আমার
ব্যক্তিগত
অভিজ্ঞতাকে
কেন্দ্র
করেই
তৈরি
করেছিলাম
ওয়ে
ব্যাক
হোম
(২০০৩)। এরপরে, পাঞ্জাব সীমান্তে দেশভাগের প্রভাব নিয়ে তৈরি করলাম হোপ ডাইস লাস্ট ইন ওয়ার (২০০৭)। ১৯৭১- এর ইন্দো-পাক যুদ্ধে ৫৪ জন ভারতীয় সৈনিককে যুদ্ধবন্দী করা হয়। তিন প্রজন্ম ধরে সেই সব সৈনিকদের পরিবারের সদস্যরা তাদের ফিরে পাওয়ার জন্য যে লড়াই করেছেন সেটাকেই ৮০ মিনিট দীর্ঘ এই ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে।
এর পরের তথ্যচিত্রটি হল ওয়াঘা (২০০৯)। প্যারেডের ডিভিডি সমাগত দর্শকদের বিক্রি করে, এমন তিনটি বাচ্চার দৃষ্টিকোণ থেকে বানানো এই ১৪ মিনিটের তথ্যচিত্র সীমান্ত এবং উগ্র দেশভক্তি প্রদর্শনের অর্থহীনতাকে স্পষ্ট করে দেয়। এর পর
কাশ্মীরের ছাত্রদের নিয়ে “গেম্স অ্যান্ড পীস” আর শেষ পর্যন্ত, “আওয়ার গ্র্যান্ডপ্যারেন্টস হোম”
(২০১৭) যে ফিল্মটি বানানোর জন্য আমি আবারও ফিরে গেছিলাম
ইন্দো-বাংলা সীমান্ত
পেরিয়ে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে উদ্বাস্তুদের যে সব জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় সেগুলোর গভীরতা ও বিস্তৃতি দর্শকদের বোঝানোর জন্যই এই তথ্যচিত্রটি আমি বানাই।

পাঞ্জাব ও বাংলা
দেশভাগের ভিন্ন চিত্র ১৯৪৭ সালে পাঞ্জাব ভাগের সময় যে ভাবে উদ্বাস্তুরা এক ঝটকায় দেশ ছেড়ে চলে এসেছিল, বাংলার ক্ষেত্রে ঠিক সেরকমটা ঘটেনি। পূর্ব বাংলা থেকে মানুষরা ক্রমে ক্রমে এদেশে এসেছিলেন। নোয়াখালি (১৯৪৬) দাঙ্গার পর থেকে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তা চলে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে। তবে, এই পার্থক্যটুকু বাদ দিলে, দেশভাগের সময় দুই জায়গাতেই বর্বরতার লক্ষণে মিল ছিল এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সম্মান রক্ষার্থে হত্যা বা “অনার কিলিং”। পুরুষতান্ত্রিকতার প্রভাবে বহু সংস্কৃতিতেই নারীর দৈহিক শুচিতার ওপরেই পরিবার বা গোষ্ঠীর সম্মান নির্ভরশীল বলে মনে করা হয়। দাঙ্গার সময় ধর্ষণ “অন্য” গোষ্ঠীর মানুষের ওপর আধিপত্য অর্জনের হাতিয়ার হিসাবে আক্ছার ব্যবহার হয়েছে।
অন্য দিকে এরকম ঘটনা ঠেকাতে ও পরিবারের মর্যাদা রক্ষার্থে, নিজেদের মহিলা সদস্যদের খুন করতেও পিছপা ছিল না অনেকে। নিজেদের বংশের রক্তের সাথে অন্য জাত বা ধর্মের রক্ত মিশে যাবে, সেই ভয় থেকেও মর্যাদার যূপকাষ্ঠে মেয়েদের বলি দেন বহু জন। অনেক মহিলা আবার নিজেরাই আত্মহত্যার পথ বেছে নিতেন। সম্মান বাঁচানোর জন্য মহিলাদের আত্মহত্যার এ রকম বহু ঘটনার খোঁজ মেলে পাঞ্জাব সীমান্তে। রাওয়ালপিন্ডিতে প্রায় ৯০ জন মহিলার কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার রিপোর্ট আমি নিজে পড়েছি।
ইন্দো-বাংলা সীমান্তে নথিবদ্ধ এরকম মৃত্যুর কোন কাহিনীর সন্ধান অবশ্য আমি পাইনি। তবে, এটা বলা ঠিক হবে না যে বাংলায় মহিলাদের ওপর এই ধরণের কোন নির্যাতনই হয়নি। আমার বাবা ১৯৫০ সালে বরিশালে হওয়া দাঙ্গার সময় তার অভিজ্ঞতার কথা ওয়ে ব্যাক হোমে বলেছেন। এক রাতের ঘটনা বাবার স্পষ্ট মনে ছিল। তিনি বলেছিলেন, "শেষ অবধি মহিলাদের সম্মানটুকুও আমরা রক্ষা করতে পারব কিনা সেই নিয়ে অনেকের মনেই সংশয় ছিল। পাঞ্জাবে মহিলাদের সাথে যা, যা ঘটেছে এখানেও তাই হবে ভেবে তারা বলাবলি করেছিল, 'পার্টিশন হবার সঙ্গে, সঙ্গে দেশ না ছেড়ে আমরা বিরাট ভুল করে ফেলেছি। এর মাশুল আমাদেরই দিতে হবে। আমাদের বাড়ির মহিলাদের ইজ্জত ওরা নষ্ট করার আগে আমরাই ওদের মেরে ফেলব', কিন্তু এর সঙ্গে, সঙ্গেই একটা মিটিং ডাকা হয় আর এই হিংসাত্মক পরিকল্পনা বাতিল করে দেওয়া হয়।"
বাবার কথা অনুযায়ী সেখানেই এই ঘটনার ইতি হয়। তবে, ইন্দো-বাংলা সীমান্তের কোথাওই যে এরকম হয়নি সেটা জোর দিয়ে বলা যাবে না। সীমান্তের এপারে অনেক মহিলার ওপরই এই ধরণের অত্যাচার হয়েছিল। আমার মনে হয় বাংলার উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সব তথ্যপ্রমাণ গোপন করেছেন। এরকম পৈশাচিক ঘটনা সবার সামনে প্রকাশ হওয়ার চেয়ে নৈঃশব্দ্যই তাদের কাছে শ্রেয় বলে মনে হয়েছে। স্মৃতি সংরক্ষণের এও এক পুরুষতান্ত্রিক পথ।
পাঞ্জাবের তুলনায় বাংলায় দেশভাগের সময়কার ঘটনাবলী নিয়ে লেখালেখির চল অনেক পরে শুরু হয়েছে। আমি যখন ওয়ে ব্যাক হোম বানানো শুরু করেছিলাম তখন পার্টিশন নিয়ে লেখা কতটুকুই বা ছিল? আমার মতে ইতিহাসকে নথিবদ্ধ করার প্রতি এই বিরাগের কারণ গুলো খুব মিশ্র। এর মধ্যে অর্থনৈতিক বা সামজিক অবনয়ন এর জন্য লজ্জা, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে যারা সাম্প্রদায়িক ও জাতি গত কারণের শোষণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশীদার ছিলেন তাদের মধ্যেকার পাপবোধ, তীব্র জীবন সংগ্রামের কারণে স্মৃতিকে ব্যাখ্যা করে লিপিবদ্ধ করার মত অবাকাশ না মেলা, প্রগতিশীলদের একটা অংশের মধ্যে দেশভাগের ইতিহাস চর্চা দাঙ্গার স্মৃতি উসকে দিতে পারে এই ভয়।
সব মিলিয়ে দেশভাগের স্মৃতিকে এড়িয়ে চলার একটা গভীর অসুখ শিল্পী, সাহিত্যিক, গবেষক মহলকে দীর্ঘদিন অসাড় করে রেখেছিল। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যেমন হিন্দুদের নির্মম অত্যাচার করে এদেশে পাঠানো হয়েছিল, বিহার বা বাংলা থেকে মুসলিমদের ঠিক একইভাবে বসতিচ্যুত করা হয়। সেই কাহিনীগুলো কোথায় হারিয়ে গেল? আমরা পাঞ্জাবের দাঙ্গা নিয়ে কথা বলি ঠিকই কিন্তু দিল্লির দাঙ্গায় মুসলিমদের ওপর হওয়া অত্যাচার নিয়ে একটা শব্দও খরচ করি না। আগে যেখানে কলকাতার অধিবাসীদের মধ্যে ৫০% মানুষ ছিলেন মুসলিম, এখন সেটা ১০-১৫% এর বেশি নয়। কেউ কখনো ভেবেছে যে বাকিরা কোথায় গেলেন?

দেশভাগ ও লিঙ্গবৈষম্য: পৃথক অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকারী নারী ও পুরুষ!
আরেকটা উল্লেখযোগ্য জিনিস আমি আমি লক্ষ্য করেছি যে দেশভাগের অভিজ্ঞতা নিয়ে নারী এবং পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রায়শই একটা ফারাক দেখা যায়। বেশির ভাগ পুরুষের স্মৃতিও কমবেশি একই ধরনের। আমার বাবা যেমন রাজনৈতিক গোলযোগ, দেশভাগের দিনক্ষণ, দাঙ্গার স্থান-কাল-পাত্র ইত্যাদি নিয়েই কথা বলতেন। এ ছাড়া, দাঙ্গার ভয়াবহতা এবং মানুষের ওপর মানুষের করা হিংস্রতার খুঁটিনাটি দিকগুলোও তিনি জানিয়েছিলেন আমায়। পরিসংখ্যানগত দিকগুলো পেরিয়ে এই স্মৃতিচারণা মোটেও সমস্যার আরো গভীরে প্রবেশ করে না। মানুষের পারিবারিক বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে ইতিহাস কথা বলে না।
আমার ডকুমেন্টারির জন্য যেসব মহিলাদের ইন্টারভিউ করি তাঁদের সাথে কথা বলে মনে হল যে দেশভাগকে তারা দেখেছেন এক ভিন্ন আঙ্গিকে। আমার মতে নিজের মাতৃভূমিকে একজন মহিলা বা পুরুষ যেভাবে মনে রাখেন সেই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে লিঙ্গের/লিঙ্গভিত্তিক আত্মপরিচয়ের এক সুগভীর সম্পর্ক আছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ, স্থানীয় মাঠ, রাস্তা, বাড়িঘর, উৎসব, অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি এবং মনের টান, আমার মায়ের জন্মভূমির সাথে যোগসূত্র ছিল এগুলোই। হোপ ডায়িস লাস্ট ইন ওয়ারেও মহিলারা পাকিস্তানের সমালোচনা করেননি, দেশভাগের নেপথ্যে থাকা রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিকেই আঙুল তুলেছেন। পাকিস্তানের দোষগুলো জানানোর সাথে, সাথে ভারত সরকারের অমানবিকতা এবং উদাসীনতার দিকগুলোও উল্লেখ করেছেন তাঁরা।
আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় দেশ যা বলে সেই বিধিবদ্ধ আখ্যানের সীমানা বহু ক্ষেত্রেই অতিক্রম করতে পারেন নারীরা। রাষ্ট্র যখন সাম্প্রদায়িক আখ্যানের কাহিনী শোনাচ্ছে, আমার মা জানিয়েছিলেন সহাবস্থানের এক ভিন্ন গল্প। হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যের ঐক্য যে সোনার পাথরবাটি নয়, বাস্তবেও তার অস্তিত্ব ছিল, সেকথা মা ভালোই জানতেন। তিনি নিজের চোখেই সেটা দেখেছিলেন।
পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত হয়ে যারা এই দেশে চলে আসেন তারা মুসলিম বিদ্বেষী হবেন, এরকম একটা ধারণা আছে। তবে, আমার মায়ের ক্ষেত্রে এর উল্টোটাই ছিল সত্যি। শুধু আমার মা'ই নয়, আরো অনেকেই কিন্তু মুসলিমদের প্রতি রাগ পোষণ করেননি। আসলে, সাম্প্রদায়িকতা পেরিয়ে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেও যে দেশভাগকে দেখা যায় সেটা বেশিরভাগ নারীই জানেন।
দাঙ্গার সময় যে গণহত্যা খোদ কলকাতায় ঘটেছিল সেটাই বা কম কী! আগুন লাগিয়ে দেওয়া, জোর করে ধর্ম পরিবর্তন, অপহরণ, ধর্ষণ থেকে শুরু করে নির্মমভাবে হত্যা, কোনটাই বাদ ছিলনা। কিন্তু মহিলাদের জবানবন্দিতে শুধু এগুলোর কথাই উঠে আসেনা। আওয়ার গ্র্যান্ডপ্যারেন্টস হোমে আহমদী বেগম তার নাতনী তুনাজ্জিনা শাহ্রিনকে নিয়ে কলকাতায় ফেরেন ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময় ৬ বছর বয়সে, ৮ রামচন্দ্র ঘোষ লেনের যে বাড়ি থেকে চলে গেছিলেন সেটিকে আরেকবার দেখবেন বলে। আহমদী বেগম জানান যে মিনার্ভা থিয়েটারটা ছিল তার কাকার। বিগত দিনের বর্বরতার বদলে, কানা কেষ্ট'র জলসা, অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, সরযূবালা এবং মলিনা দেবীর নাট্যাভিনয় নিয়ে কথা বলতেই তিনি বেশি আগ্রহী ছিলেন। থিয়েটারে পা রাখতেই তার মুখে যেন হাজার ওয়াটের আলো জ্বলে উঠেছিল। ওখানে শাহজাহান ও চাঁদসদাগরের মতন নাটক দেখবার কথা তার মনে পড়ে গেছিল।
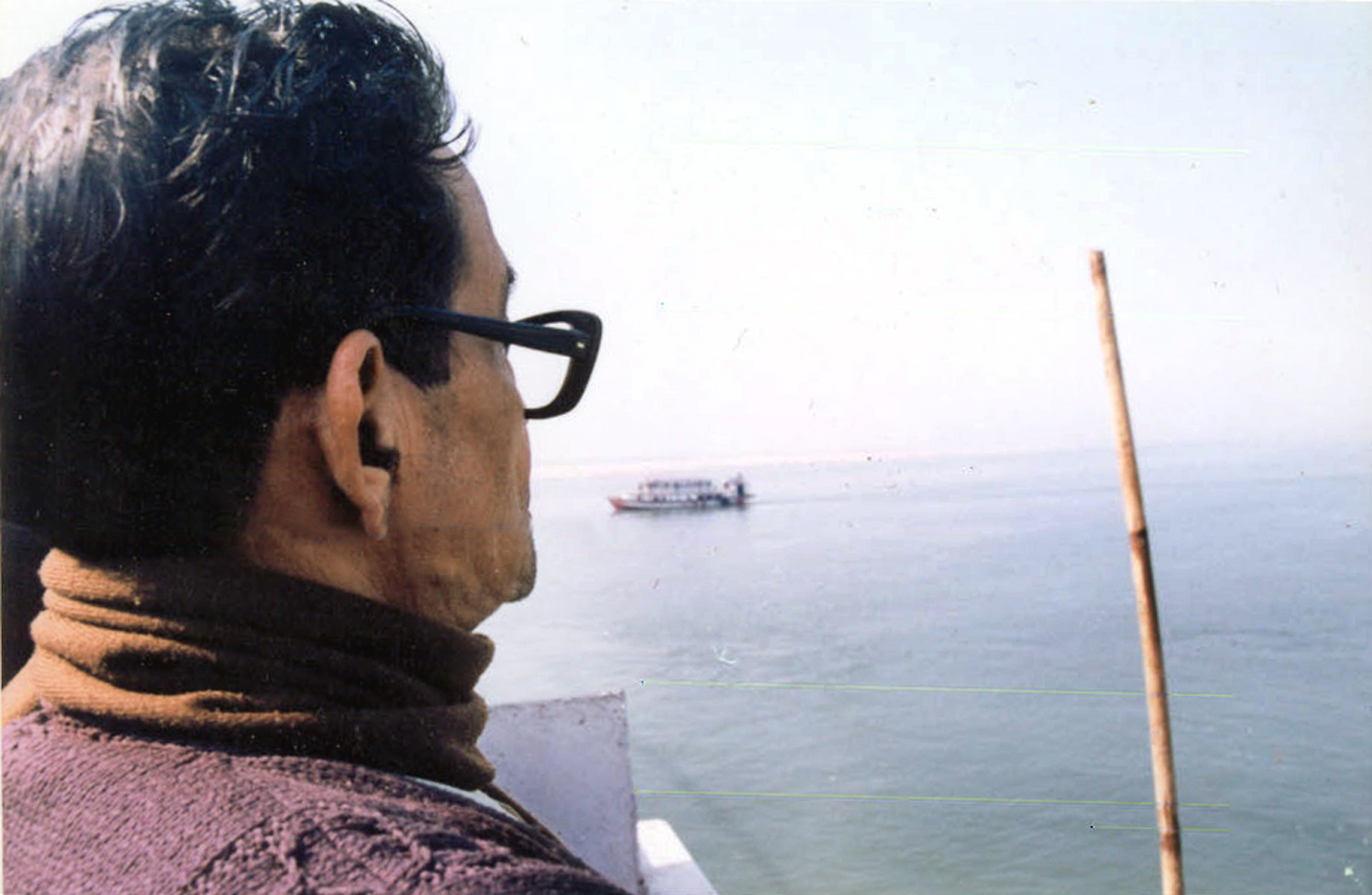
আমার মাকেও দেখেছি স্মৃতিচারণের সময় ধর্মীয় হিসেবনিকেশকে দূরে সরিয়ে রাখতে। মুসলিম প্রতিবেশীরা দেশ ছেড়ে পালানোর সময় তাকে কতটা সাহায্য করেছিলেন সেকথা মায়ের মুখে অনেকবারই শুনেছি। অভিজ্ঞতার এই দিকটা মা চাইলেই আড়াল করতে পারতেন কিন্তু সেটা তিনি চাননি। বাংলাদেশে ফিরে গিয়েও সেই মুসলিম প্রতিবেশীদের নাম ধরে, ধরে খোঁজ করেছিলেন মা। মা বলেছিলেন বেনাপোল বর্ডার দিয়ে এদেশে চলে আসার সময় এক মুসলিম কাস্টম অফিসার তাদের নিরাপদে পৌঁছে দিতে সঙ্গে এসেছিলেন। মায়ের মুখ থেকে তার বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া তুতো দিদি কমলি মাসীর কথা শুনলে তিনি যে সাম্প্রদায়িক হিংসার সীমিত গণ্ডি পেরিয়ে এগিয়ে এসেছেন সেটা আরো স্পষ্ট হয়ে যায়।
ছোট থেকেই আমি মায়ের কাছে কমলি মাসীর অনেক গল্প শুনে বড় হয়েছি। মা কমলি মাসীর খুব প্রশংসা করতেন যেমন মাসীর কোঁকড়ানো চুল ছিল দেখার মতন, তিনি গান ভালবাসতেন আবার নিজেও দারুণ গান গাইতেন। মা একথাও জানিয়েছিলেন যে একজন মুসলিমকে ভালোবেসে বিয়ে করার কারণে কমলি মাসী নিজের পরিবার থেকে বিতাড়িত হন। আমার মায়ের মতে কমলি মাসী ভুল কিছু করেননি। মায়েদের পরিবার যখন ভারতে চলে আসে তখন কিন্তু কমলি মাসীকে তারা সঙ্গে আনেনি। গোটা দুনিয়া যাই ভাবুক, মা বাংলাদেশ গিয়ে কমলি মাসীর সাথে একবার অন্তত দেখা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। দুঃখের ব্যাপার হল আমাদের যাওয়ার ঠিক আগের বছরেই কমলি মাসী মারা যান। আমার মাসতুতো বোন মিনু ওরফে নাজমুন হক (কমলি মাসীর মেয়ে)র সাথে আমাদের প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্তগুলো আমাদের কাছে খুবই মূল্যবান। মিনু কমলি মাসীর ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে যা, যা বলেছিল মা খুব মন দিয়ে, ধৈর্য্য সহকারে শুনেছিলেন। কমলি মাসীর কবরে মা তাঁকে স্মরণ মা তাঁকে স্মরণ করে একটা মোমবাতি জ্বেলেছিলেন।
সীমান্তের উপাখ্যান এবং শিশুরা
আমার বানানো ডকুমেন্টারিগুলোর মধ্যে তিনটিকে অনেকে ট্রিলজি বলে মনে করেন। ওয়ে ব্যাক হোম পেছন ফিরে অতীতের দিকে তাকায়, হোপ ডায়িস লাস্ট ইন ওয়ার বর্তমান সময়কে তুলে ধরে। শিশুদের দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি ওয়াঘা কিন্তু আগামীর বার্তাবহ। ওয়াঘা বানানোর সময়ই বুঝতে পারি যে সীমান্ত এবং দেশভাগ নিয়ে শিশুদের মনোভাব প্রাপ্তবয়স্কদের চেয়ে অনেকটাই আলাদা। ওদের কাছে এগুলো হাস্যকর আর মেকি। যেহেতু প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলেই ওরা বর্ডার পেরিয়ে অন্য প্রান্তে চলে যায় আর সেখানে বিপদের দিনের আশ্রয়টুকু ঠিকই জুটে যায় তাই ওদের কাছে বর্ডার নিছকই অর্থহীন। কাশ্মীর নিয়ে দুই দেশের বিবাদ হোক বা ওয়াঘা বর্ডারে সৈন্যদের বিটিং রিট্রিট সেরেমনি, বাচ্চাদের কাছে সবটাই প্রহসন মাত্র।
একটু তলিয়ে ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে ওদের চিন্তাভাবনায় কোন ভুল নেই। মানব সভ্যতার গোড়া থেকেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মানুষের চলাচল ছিল যাপনের অঙ্গ বিশেষ। তাই, আজকের দিনে কাঁটাতার দিয়ে মানুষকে আটকে রাখার মরণপণ চেষ্টার গোটা বিষয়টাই পরিহাসজনক। স্মৃতিদের সাথে সমঝোতা তথ্যচিত্র বানানোর সময় স্মৃতিগুলোকে পর্দায় কিভাবে আর কতটা ফুটিয়ে তোলা যায় সেই সিদ্ধান্তের ওপরে অনেক কিছুই নির্ভর করে।
কট্টরপন্থীরা যখন জানতে পারে আমি দেশভাগ নিয়ে তথ্যচিত্র বানাচ্ছি, তখন তারা আশা করেছিল যে দুই জাতির মধ্যের ঘৃণার আগুনে আমি নিশ্চই ঘৃতাহুতি দেব। আমি যে স্মৃতির হাত ধরে সাম্প্রদায়িক বিভেদ মুছে দিতে চাইছি এই বিষয়টা তাদের মোটেও মনঃপূত হয়নি। আমি কখনোই এটা প্রমাণ করবার পক্ষপাতী ছিলাম না যে দেশভাগের জন্য শুধুমাত্র একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হোপ ডায়িস লাস্ট ইন ওয়ারের মতন একটি তথ্যচিত্রে পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা বেশ কঠিন কাজ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কাজটা আমি করেছিলাম। যাদের পরিবারের সদস্যদের আজো কোন খোঁজ মেলেনি তারা নিজেরাই বলেছেন যে শুধু পাকিস্তান আমাদের নাগরিকদের আটক করে রাখেনি, সেই একই কাজ ভারতও পাকিস্তানি সেনাদের ছাড়েনি।
যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে একজনের পরিবারের সদস্য আমার কাছে আক্ষেপ করে বলেন বাবা দেশের জন্য শহীদ হয়েছেন, এই কথাটা কোন ছেলে মেনে নিতে পারে না। আমার তথ্যচিত্রের মাধ্যমে তিনি প্রশ্ন করেন "রাষ্ট্র বা সেনাবাহিনীর কাছে এটা হয়ত গর্বের, কিন্তু পরিবারের পক্ষে কি এটা মেনে নেওয়া সম্ভব?"এই প্রসঙ্গ উত্থাপনের কারণ হল ১৯৭১-এর যুদ্ধে লড়েছিলেন এমন ৫২ জন যুদ্ধবন্দীর খোঁজ এখনও অবধি পাওয়া যায়নি। আমি মনে করি অতীত স্মৃতির যে অংশ বৈষম্য, অত্যাচার আর রক্তপাতের সঙ্গে যুক্ত তার সাথে বর্তমানের একটা সদর্থক সমঝোতা হওয়া দরকার। নাহলে বর্তমান সময়ে আমরা শান্তি বা স্থিতি অর্জন করতে পারবনা। তাই, আমার সিনেমায় আমি কোন ঘৃণামূলক উক্তি, বিদ্বেষমূলক বার্তা রাখি না। তবে, এর জন্য যে সত্যের সাথে আপোস করেছি এমনটাও নয়।
এটা ঠিক যে পরিচালক হিসেবে আমার নিজস্ব ভাবনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সাক্ষাৎকারগুলিকে বিষয়ের জন্য বেছে নিয়েছি। মানবিক মেলবন্ধনের গল্পই আমার ছবিতে প্রাধান্য পেয়েছে। অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার দময়ন্তী তাম্বে, যার স্বামী ফ্লাইট লেফট্যানেন্ট ভি ভি তাম্বে ১৯৭১ সালের ইন্দো পাক যুদ্ধের ৫৪ জন নিখোঁজ যুদ্ধবন্দিদের একজন, তার জবানবন্দি আমি কিন্তু একটুও কাটিনি বা বদলাইনি। তিনি বলেছেন, "দেশের আসল নায়করা বাড়ি ফিরতে চান। তাদের আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন। আপনাদের নিরাপত্তার জন্য তারা লড়াই করেছিলেন, তাই তাদের মুক্তির জন্য এবার আপনাদের লড়াই করা উচিত।" এত বঞ্চনার পরেও বছর পরেও দময়ন্তী যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা বা সৈন্যবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে রাষ্ট্রের তৈরী অনেক ন্যারেটিভেই বিশ্বাস রাখেন। তার অনেক কিছু বিশ্বাস আমার ধ্যান ধারনার পরিপন্থী। কিন্তু তা সত্বেও আমি আমার ছবিতে ওনার জবানবন্দি অপরিবর্তিত রেখেছি, নিজের মতের সাথে তার মতকে জোর করে মেলানোর চেষ্টা করিনি।

ব্যক্তিগত স্মৃতিদের জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ
তথ্যচিত্র বানানোর জন্য প্রথমেই কাহিনীর মুখ্য চরিত্রদের বিশ্বাস অর্জন করাটা জরুরি নাহলে তারা সহজে নিজেদের ব্যক্তিগত কথা বলতে চান না। হোপ ডায়িস লাস্ট ইন ওয়ারের জন্য আমি যে পরিবারগুলোর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল অন্য রকম। আগেও সংবাদমাধ্যমে তাদের বিষয়ে চর্চা হয়েছিল। তবে, মিডিয়ার সাথে কথা বলার অভিজ্ঞতা তাদের কাছে ছিল প্রতারণারই সমতুল্য। প্রত্যেকবার ইন্দো-পাক সম্পর্ক শিরোনামে এলেই সংবাদমাধ্যমে তাদের বিপন্নতাকে জাহির করা হত কিন্তু খবর যেই বাসি হয়ে যেত, লোকেও সহজেই তাদের ভুলে যেত। ডকুমেন্টারি বানানোর জন্য তাদের সাথে কথা বলতে যেতে ওনারা ধরে নিয়েছিলেন আমিও একই রকম কিছু একটা করতে চলেছি। কিন্তু দময়ন্তী তাম্বের সাথে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর তিনি বুঝতে পারেন যে আমার ওরকম কোন হীন উদ্দেশ্য নেই। তিনি আমার আগেকার কাজের কথা জানতে পারেন এবং দূরের শহর কলকাতার একজন পরিচালক এরকম একটা তথ্যচিত্র বানানোর জন্য কষ্ট সহ্য করতে রাজি সেটাও উনি বেশ বুঝে যান। দুই দেশই আটক যুদ্ধবন্দিদের স্বদেশে ফেরত পাঠাবে একথা ঠিক দু'দিন আগেই আমি জানতে পারি। খবরটা পাওয়া মাত্র ক্যামেরা নিয়ে কোলকাতা থেকে পৌঁছে গেলাম অমৃতসরে।
যুদ্ধবন্দিদের পরিবারের সদস্যরা বুঝতে পারলেন যে ফিল্মটি বানানোর ব্যাপারে আমি আন্তরিক। এভাবেই তারা বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমাকে আপন করে নিয়েছিলেন। আমি তাদের যে ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতাম তার থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছিল যে তাদের জীবনের গল্প বেচে অর্থ উপার্জন করাটা আমার উদ্দেশ্য নয়। ওনারা ক্রমেই বুঝতে পারেন যে আমি শুধুমাত্র ওনাদের দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাসকে শৈল্পিক ভঙ্গিতে সবার সামনে তুলে ধরতে আগ্রহী। ওঁরা ধীরে ধীরে সমস্ত স্মৃতি, গল্প আর অনুভূতিরা ভাণ্ডার খুলে ধরেন আমার কাছে। দময়ন্তী তাম্বে বলেছিলেন১৯৭১ এর যুদ্ধে ওনার ফাইটার পাইলট স্বামী হারিয়ে যাবার পড় প্রথম ছয় মাস ধরে তিনি শুধু কেঁদেছেন। এমনকি জ্যোতিষীদের কাছেও ধর্না দিয়েছেন। তারপরে, একদিন নিজেই কান্না মুছে ঘুরে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতির সাথে লড়াই করবার সিদ্ধান্ত নেন। শ্যুটিংয়ের শেষ দিনে সেই দময়ন্তী তাম্বের চোখে জল দেখলাম। আমার ডকুমেন্টারিতে সেই দৃশ্য ধরে রাখতে পেরেছিলাম।
আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনি নববিবাহিত ছিলেন, নিজের শারীরিক, মানসিক চাহিদার বিষয়কে কিভাবে দমন করতে পারলেন? ওনার পক্ষে এরকম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ ছিলনা। একে তো আমি পুরুষ তায় বয়সে ওনার তুলনায় অনেকটাই ছোট। তা সত্বেও উনি সহজাত গাম্ভীর্য বজায় রেখেই জানিয়েছিলেন যে চাওয়াপাওয়ার সমস্ত অনুভূতিকে উনি বোতল বন্দী করে ফেলেছিলেন সারা জীবন ধরে স্বামীকে ফিরে পাবার লড়াই চালিয়ে যাবার জন্য। এই ধরণের একান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন করার নেপথ্যের কারণটা কিন্তু বাদবাকিরাও বুঝে নিয়েছিলেন। ফ্লাইট লেফট্যানেন্ট সুধীর গোস্বামীর স্ত্রী পুনম গোস্বামী আমায় অকপটে বলেছিলেন যে প্রথমবার স্বামীকে ইউনিফর্মে দেখেই তিনি প্রেমে পড়ে গেছিলেন। বাগদান থেকে শুরু করে বিয়ে আর মধুচন্দ্রিমার ছবিও উনি আমাকে দেখান। দম্পতির মধ্যের স্বাভাবিক অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় সমৃদ্ধ স্বামীর লেখা শেষ চিঠিটি উনি ক্যামেরার সামনেই পড়ে শোনান।
ওনাদের জীবনের আখ্যান শুনে আমি বুঝতে পারি যে এক অসমাপ্ত জীবন যাপনের যন্ত্রণা কতটা প্রগাঢ় হতে পারে। কিন্তু এই পরিবারগুলো থেকে হারিয়ে যাওয়া মানুষদের পরিণতি কী হয়েছে তা আজও অমীমাংসিত। সময়ের জালে তাঁরা তাই আটকা পড়েছেন। কেউ, কেউ হয়ত জীবনের পথে এগিয়ে গেছেন। বেশির ভাগই অতীত আঁকড়ে ধরেই বেঁচে থেকেছেন।
অপ্রকাশিত গল্পগুচ্ছ
একদিন এক প্রবাসী মহিলা ফোন করে যা বললেন শুনে রীতিমত চমকে গেলাম। এটা হল হোপ ডায়িস লাস্ট ইন ওয়ার বানানোর কিছু বছর পরের ঘটনা। উনি আমায় বললেন যে আমার বানানো ডকুমেন্টারি দেখে উনি হতচকিত হয়ে গেছেন। আমার ওনার বলা প্রত্যেকটা শব্দ মনে আছে,"আমি এটা জেনেই বড় হয়েছি যে আমার বাবা ১৯৭১ এর যুদ্ধে মারা গেছেন। আমার মা আবার বিয়ে করেন। আপনার ডকুমেন্টারি দেখে জানলাম যে আমার বাবা একজন যুদ্ধবন্দী!" টাইম ম্যাগাজিনে একটি নিবন্ধের সঙ্গে প্রকাশিত কারাগারে আটক ভারতীয় বন্দীদের কিছু ছবি ওই ডকুমেন্টারিতে আমি দেখিয়েছিলাম। তাদেরই মধ্যে একজন সম্ভবত ওই ভদ্রমহিলার বাবা! তিনি যখন জানলেন যে তার বাবা সরকার ঘোষিত “শহীদ” নন বরং সম্ভবতঃ তখনো বেঁচে থাকা একজন যুদ্ধবন্দী তার আজীবন লালিত ধারণাগুলো ওলটপালট হয়ে যায় এবং তিনি অপরিসীম মানসিক যন্ত্রণার শিকার হন।
যে কোন মানুষই যখন জানতে পারে যে তার বিশ্বাসগুলো ভিত্তিহীন, তখন জীবনের সরল হিসেবনিকেশ সবই যায় গুলিয়ে। তথ্যচিত্র বানানোর সময় ভিন্ন গল্পের মোড়কে বারংবার মৃত্যুর সাক্ষাৎ পেয়েছি। পূর্বোল্লিখিত কাহিনীটি যেন অনিশ্চয়তা নিয়ে লেখা অধ্যায়ের প্রথম পাতা। অন্যদিকে, আমার বাবা শান্তির খোঁজে বরিশালের সেই শ্মশানে যান যেখানে তার কলেরায় মৃত পাঁচ বছরের ভাই নিমাইকে কবর দেওয়া হয়েছিল (হিন্দু পরিবারের শিশুরা মারা গেলে তাদের কবর দেওয়ারই প্রচলন ছিল)। বাবার মুখে শুনেছিলাম যে এক ঝড় জলের দুপুরে, মৃত ভাইকে কোলে করে বাবা ওইখানে নিয়ে গেছিলেন। যখন শিশুটিকে কবর দেওয়া হচ্ছিল তখন মাথার ওপরে পাক দিচ্ছিল এক দল শকুন। তখন বাবার বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। বাবা যখন অতীতের স্মৃতি হাতড়াচ্ছিলেন, আমার খালি মনে হচ্ছিল যেখানে এককালে ভাইকে কবর দিয়েছেন সেই মাটি এখন আর বাবার দেশ নয়, এই সত্য কতটা দুর্বহ!
আওয়ার গ্র্যান্ডপ্যারেন্টস হোম শ্যুট করার সময় যখন আহমদী বেগমের সাথে কলকাতায় তার ছোটবেলার স্মৃতি বিজড়িত বাড়িটিতে ফিরে যাই, সেই অভিজ্ঞতা আমায় গভীরভাবে ঋদ্ধ করেছিল। সেই বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ার সময় এখনকার মালিক কি ভাববেন সেই চিন্তায় তিনি অস্থির। "আশা করি আমি এভাবে এখানে এলাম বলে কেউ কিছু বলবে না...", ওনার এই একটা কথাই আমায় বুঝিয়ে দেয় যে দেশভাগ উদ্বাস্তুদের মনেও এক অদৃশ্য সীমারেখা টেনে দিয়েছে। জন্মভূমি ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় তাঁদের আর কী বা বয়স ছিল! কোনদিন ফিরে আসতে পারবেন কিনা সেটুকুও জানতেন না। তাই, যতদিনে সত্যিই ফিরে এলেন, পূর্বের অভিজ্ঞতার নিদারুণ যন্ত্রণার শেকড় এতটাই দৃঢ ভাবে মনজমিন আঁকড়ে ধরেছে যে নিজেকে তার অনাহূত বলেই মনে হচ্ছিল। আমার মনে হয় দেশভাগের অভিজ্ঞতা নিয়ে বেঁচে থাকা মানুষদের গল্পগুলো বলা, শোনা এবং দেখাটা দরকার। তাদের অভিজ্ঞতার নক্সীকাঁথা অনুভবের সুতোয় বোনা আর সেই সুতোর রং বড়ই পাকা। "আমরা এবং ওরা" এই গণ্ডি ভেঙে, স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে রটানো অর্ধসত্য পায়ে দলে, সীমান্তের আসল সত্যিটা বুঝতে হবে আমাদের।
এমনিতেও অনেকটা দেরি হয়ে গেছে! এখন সময় অতীতকে ফিরে দেখার। এবং, আরেকটু তলিয়ে ভাবার।

