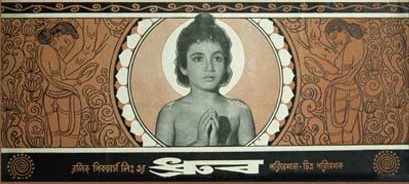'অপুর সংসার' ছবির একটি দৃশ্য
সিনেমার আর্কাইভ, 'অপুর সংসার' ও সত্যজিৎ রায়
তারিখ : 02-May-2024
ছবির ভেতর ছবি: ফিল্ম সংরক্ষণের অসামান্য দৃষ্টান্ত সত্যজিতের 'অপুর সংসার'
চলচ্চিত্র শৈল্পিক অভিব্যক্তি হবার মর্যাদা পাওয়ার পর থেকেই জোরকদমে শুরু হয় এর সংরক্ষণের কাজ।আগেকার দিনে সিনেমাপ্রেমীরা সাধারণত পছন্দের ফিল্মের ভিসিআর সংগ্রহে রাখতেন। অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায় সিনেমাপ্রেমী হিসেবেও অনুরাগীদের কাছে সুপরিচিত। তিনি তাঁর নিজের তৈরি 'অপুর সংসার' ছবির মাধ্যমে আরেকটি ছবিকে অমরত্ব প্রদান করেন। সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর অভিনব সিনেমা সংরক্ষণ প্রয়াসের সাক্ষ্য দিলেন স্রগ্ধরামালিনী দাস।
বিএফএ এই কাজের দায়িত্ব নিল কেন?
সত্যজিৎ রায়ের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়েই এযাবৎ চর্চা হয়েছে। একজন যথার্থ শিল্পীর দক্ষতায় কিভাবে বিশ্ববিখ্যাত এই পরিচালক তাঁর অপুর সংসার ছবিটিকে আরো অর্থবহ করে তোলেন এক পৌরাণিক ছবির সহায়তায় সেবিষয়ে জানতে এবং জানাতে চেয়েই আমরা সর্বসমক্ষে এই নিবন্ধটি নিবেদন করলাম।
নব্য ভারতীয় জাতি-রাষ্ট্রে সিনেমা একটি গুরুত্বপূর্ণ শৈল্পিক ও সাংস্কৃতিক মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া মাত্রই এটির সংরক্ষণের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া শুরু হয়। এর ফলশ্রুতি স্বরূপ ১৯৬৪-সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ অফ ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হবার পাশাপাশি ১৯৭০- এর দশকে ভিসিআর সংগ্রহের মাধ্যমে ব্যক্তিগত পরিসরে অনেকেই সিনেমা সংরক্ষণের উদ্যোগ নেন। এই ধরণের প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইচ্ছানুযায়ী আসল সিনেমাটি দেখার সুবিধা উপভোগ করা ও সেটির সংরক্ষণ। এরপরে, ১৯৯০- এর দশকে ইন্টারনেট পরিষেবার উত্থান এবং বিভিন্ন ইন্টারনেট ভিত্তিক সংযোগ মাধ্যমের ক্রমবিকাশের ফলে সিনেমাপ্রেমীরা সহজলব্ধ উৎস উপাদানগুলির সৃজনশীল ব্যবহারে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এই নতুন ভাবনা একদিকে যেমন পুরানো ও সমসাময়িক ফিল্মের বিশেষ, বিশেষ কিছু দৃশ্য ভাগ করার প্রবণতায় প্রকাশ পায় তেমন অন্যদিকে নির্মাতার ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন ছবির সমগোত্রীয় রীতির দৃশ্যাবলীর সংকলন তৈরির মাধ্যমেও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই ধরণের পোস্টমিলেনিয়াল ভিডিও ক্লিপসগুলি সংরক্ষণের প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলীর পরিপন্থী হওয়া সত্বেও সিনেমার শৈল্পিক গুরুত্বকে একইভাবে তুলে ধরতে চায়। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় কিন্তু তাঁর দূরদর্শিতার জোরে ১৯৫০-এর দশকের শেষের দিকেই ফিল্মের মধ্যেই ফিল্ম সংরক্ষণের এক অভিনব পরীক্ষামূলক নজির স্থাপন করেন যার কথা অনেকেরই অজানা। তাঁর প্রথমদিকের কাজগুলির মধ্যে অন্যতম ‘অপুর সংসার’ (১৯৫৯) ছবিটিতে এর নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। সত্যজিৎ রায় প্রোডাকশনসের দ্বারা প্রযোজিত প্রথম এই ছবিটির সাথে পরিচালক ‘ধ্রুব’ (১৯৫৩) নামক ছবিটির একটি সংযোগ স্থাপন করেন।

'ধ্রুব' ছবির দৃশ্য, 'অপুর সংসার' ছবিতে ব্যবহৃত
'ধ্রুব'র সংরক্ষণমূলক ব্যবহার
সমসাময়িক চিত্রনির্মাতা চন্দ্রশেখর বসু পরিচালিত 'ধ্রুব' ছবিটি বিষ্ণু পুরাণে বর্ণিত সমনামের চরিত্রের (বিভু ভট্টাচার্য অভিনীত) জীবনকাহিনী দৃশ্যায়িত করে। রাজা উত্তানপদ (অজিতপ্রকাশ) এবং তাঁর পরিত্যক্ত স্ত্রী সুনীতির (বাণী গঙ্গোপাধ্যায়) সন্তান ধ্রুব বাবার কাছ থেকে যথোপযুক্ত স্নেহের পরিবর্তে উপেক্ষা পাওয়ায় ব্যথিত হৃদয়ে মা'কে ছেড়ে আধ্যাত্মিক পিতা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। অদম্য মনের জোর এবং কঠোর তপস্যার বলে ধ্রুবর দেব ও দানবের চক্রান্তের জাল ভেদ করে বিষ্ণুকে তুষ্ট করা এবং বর হিসেবে ধ্রুবতারা রূপে অমরত্ব প্রাপ্তি তথা চিরস্মরণীয় হয়ে ওঠার কাহিনী জানায় এই ছবিটি। সত্যজিৎ রায়ের অপুর সংসার ছবির মাঝামাঝি অংশে দেখা যায় গল্পের মুখ্য চরিত্র অপূর্ব/অপু (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) এবং তাঁর স্ত্রী অপর্ণা (শর্মিলা ঠাকুর) সিনেমা হলে 'ধ্রুব' ছবিটি দেখতে গেছে।
যদি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'অপরাজিত' (১৯৩১) উপন্যাসটির পাতা উল্টে দেখা যায় তাহলে সহজেই সেটি অবলম্বনে তৈরি সত্যজিৎ রায়ের সিনেমার সাথে উপন্যাসের ফারাক ধরা পড়বে।
যদি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'অপরাজিত' (১৯৩১) উপন্যাসটির পাতা উল্টে দেখা যায় তাহলে সহজেই সেটি অবলম্বনে তৈরি সত্যজিৎ রায়ের সিনেমার সঙ্গে উপন্যাসের ফারাক ধরা পড়বে। সত্যজিৎ প্রায় এক মিনিট ধরে থিয়েটারে ছবিটি দেখার দৃশ্য তুলে ধরলেও বিভূতিভূষণের লেখায় পুরাণ নির্ভর 'ধ্রুব' ফিল্মটির কোন উল্লেখই পাওয়া যায়না। বিভূতিভূষণের গল্পের সূত্রধর দু'লাইনে শুধু এটুকুই জানায় যে অপু বেশ কয়েকবার অপর্ণাকে থিয়েটার দেখতে নিয়ে গেছে কিন্তু কোন ছবি তারা দেখেছে সে বিষয়ে কোনরকম আলোকপাত করেনা। এই সামান্য তথ্যকে যেভাবে সত্যজিৎ তাঁর ছবিতে ব্যবহার করেছেন সেটা চলচ্চিত্রপ্রেমী হিসেবেই তাঁকে চিহ্নিত করে।
'ধ্রুব' ছবির দৃশ্য, 'অপুর সংসার' ছবিতে ব্যবহৃত
টম গানিং প্রদত্ত আকর্ষণের সিনেমা সংক্রান্ত তত্ত্ব অনুযায়ী যে ধরণের রোমাঞ্চকর দৃশ্যাবলীর মাধ্যমে দর্শকদের আকর্ষিত করা সম্ভব সেরকম বহু দৃশ্য যেমন আকাশের বুক চিরে নক্ষত্রের সরে যাওয়া কিংবা পর্দায় দৃশ্যমান চরিত্রের মিলিয়ে যাওয়া বা রূপান্তর দেখতে পাওয়া যায় ‘ধ্রুব’ ছবিটিতে। সত্যজিৎ রায়ের এই ছবিটি বেছে নেওয়া বোধহয় নেহাতই কাকতালীয় বিষয় নয়। পরবর্তী কালে সত্যজিৎ নিজেও তাঁর 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' (১৯৬৯) ফিল্মে এই ধরণের কৌশল অবলম্বন করেন।
তা ছাড়াও বলা যায় যে ‘ধ্রুব’ ছবির দৃশ্যাবলী সত্যজিতের ছবিটিকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। দর্শকদের মনে থাকবে যে এই দৃশ্যের পরেই অপর্ণা, অপুকে ছেড়ে, তার বাপের বাড়ি রওনা দেয় এবং সেখানেই স্বামী অপু এবং সদ্যোজাত সন্তান কাজল, উভয়ের থেকেই মৃত্যু অপর্ণাকে বহু দূরে নিয়ে যায়। অপর্ণার মৃত্যুর জন্যে নিজেকেই দায়ী ভাবা অপু বহু বছর কাজলের থেকে দূরে সরে থাকে। সত্যজিৎ যেন 'ধ্রুব' ছবির বিচ্ছেদ ও বিমুখতার কাহিনীর মধ্যে দিয়ে তাঁর ছবির চরিত্রেরা বিচ্ছেদের যে দুরূহ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তারই আগাম সঙ্কেত দিয়েছেন।
উপন্যাসের বর্ণনা থেকে ভারসাম্যপূর্ণ শব্দ সম্বলিত সবাক চলচ্চিত্রে সরে গিয়ে সত্যজিৎ রায় এক্ষেত্রে কালাতিক্রমণ করেছেন এবং এটিই তার একমাত্র উদাহরণ নয়।
সংরক্ষণের মাধ্যম রূপে 'অপুর সংসার' ফিল্মটির পর্যালোচনা
একথা অনস্বীকার্য যে ধ্রুবর গল্প 'অপুর সংসার' ফিল্মটির কাহিনিবিন্যাসের সাথে মানানসই কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের সংরক্ষণ প্রয়াসের প্রভাব এটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। ভারতের প্রথম টকি ফিল্ম 'আলম আরা' এবং প্রথম বাংলা টকি ফিল্ম 'জামাই ষষ্ঠী' দু'টিই ১৯৩১-সালের পরে মুক্তিলাভ করেছিল। যেহেতু, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসটি ১৯৩১-সালে প্রকাশিত হয় তার অর্থ এটাই যে তিনি তাঁর কাহিনীতে নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগের ফিল্মেরই উল্লেখ করেছেন। বিভূতিভূষণের লেখায় বড় পর্দায় প্রদর্শিত চলমান ছবির বর্ণনার সাথে, দর্শমাধ্যমে অভিনবত্ব সৃষ্টিকারী, সিনেমার প্রথম তিন দশকে নির্মিত নির্বাক চলচ্চিত্রের মিল যথেষ্ট প্রকট। উপন্যাসের বর্ণনা থেকে ভারসাম্যপূর্ণ শব্দ সম্বলিত সবাক চলচ্চিত্রে সরে গিয়ে সত্যজিৎ রায় এক্ষেত্রে কালাতিক্রমণ করেছেন এবং এটিই তার একমাত্র উদাহরণ নয়।
'ধ্রুব' ছবির দৃশ্য, 'অপুর সংসার' ছবিতে ব্যবহৃত
সত্যজিতের পরবর্তী ছবি ‘চারুলতা’য় (১৯৬৪) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস ‘আনন্দমঠ’ (১৮৮২) উপন্যাসটির উল্লেখ চোখে পড়েছে এ বিষয়ের অন্যতম গবেষক ছন্দক সেনগুপ্তর। ‘চারুলতা’ উপন্যাসটি ১৮৭৯-৮০ সালের পটভূমিতে রচিত হওয়ায় বঙ্কিম রচিত উপন্যাসটি ফিল্মের চরিত্রদের হস্তগত হবারও কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাস যে প্রেক্ষাপটে লিখেছেন, সত্যজিৎ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উত্থানের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের হেতু সেখান থেকে কিছুটা হলেও সরে গেছেন। কালাতিক্রমণের যে নমুনা 'অপুর সংসার' ছবিতে পাওয়া যায় তার দ্বৈত গুরুত্ব আছে। প্রথমত, ‘ধ্রুব’ একটি সবাক চলচ্চিত্র হওয়ায় অপুর সংসার ছবিটির থিয়েটার দেখার দৃশ্যে শব্দের অভাব ঘটেনি যা কোন নির্বাক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হলে ঘটত। দ্বিতীয়ত, ‘ধ্রুব’ ছবির বজ্রপাতের শব্দ সম্বলিত দৃশ্যটি ব্যবহারের মাধ্যমে সত্যজিৎ রায় তাঁর অপু ট্রিলজির প্রথম ছবি ‘পথের পাঁচালী’র ধ্বংসাত্মক ঝড়বৃষ্টির কথা মনে করিয়ে দেন, যার ফলশ্রুতি স্বরুপ অপুর দিদি দুর্গার মৃত্যু ঘটে। থিয়েটারের দৃশ্যে 'ধ্রুব' ছবিটি বড় পর্দায় দেখানোর তাৎপর্য এর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়।
১৯৩৪-সালে একই পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত সমনামের (যদিও দুটি ছবির ইংরেজি বানানে সামান্য তারতম্য রয়েছে) ছবিটিকে বাদ দিয়ে সত্যজিৎ রায় কেন ১৯৫৩-সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'ধ্রুব' ছবিটি বেছে নিলেন সেটাও ভেবে দেখবার।
১৯৩৪-সালে একই পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত সমনামের (যদিও দুটি ছবির ইংরেজি বানানে সামান্য তারতম্য রয়েছে) ছবিটিকে বাদ দিয়ে সত্যজিৎ রায় কেন ১৯৫৩-সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'ধ্রুব' ছবিটি বেছে নিলেন সেটাও ভেবে দেখবার। পূর্বে নির্মিত ফিল্মটিও টকি হবার দরুণ সেক্ষেত্রেও কালাতিক্রমণ ঘটত। তাছাড়া, আধুনিক সামাজিক ছবির ক্ষেত্রে সেটের সাজসজ্জা বা লোকেশন দেখে সেটি সমসাময়িক কিনা বোঝা সম্ভব হলেও পৌরাণিক ছবির প্রেক্ষাপট হিসেবে সুসজ্জিত রাজসভা কিংবা বনভূমি ব্যবহৃত হওয়ায় সেগুলি নির্মাণের সময়কাল সেট ডিজাইন দেখে আলাদা ভাবে বোঝা যায়না। তাই, ‘অপুর সংসার’ ছবির কাহিনী যে সময়কাল সাপেক্ষে রচিত (১৯৩০ সাল ও তার পূর্ববর্তী সময়) তার প্রায় সমসাময়িক ছবিটিকে গ্রহণ করা হলে কোন বৃহত্তর অসঙ্গতি সৃষ্টি হত না। ফিল্মটির ১৯৩৪ সালে মুক্তিলাভও কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের এহেন সিদ্ধান্তের নেপথ্যের আরেকটি কারণ হতে পারে। সেই সময়কার অন্যতম সুপরিচিত থিয়েটার হল ছিল ক্রাউন থিয়েটার যেখানে 'জয়দেব' (১৯৩৩), 'রাধা কৃষ্ণ' অথবা 'কলঙ্ক ভঞ্জন' (১৯৩৩), 'সাবিত্রী' (১৯৩৩), 'শ্রী গৌরাঙ্গ' (১৯৩৩) এবং 'চাঁদ সওদাগর' (১৯৩৪) ইত্যাদি বহু পৌরাণিক ছবি প্রদর্শিত হয়। সেখানেই 'ধ্রুব' ছবিটিও মুক্তিলাভ করেছিল। তবে, খেয়াল করলেই বোঝা যাবে যে সেই সময় সত্যজিৎ রায়ের (১৯২১ সালে তাঁর জন্ম) বয়স ছিল মাত্র বারো বছর। সত্যজিতের জীবনীকার অ্যান্ড্রিউ রবিনসনও স্কুলজীবনে তাঁর হলিউডের বিভিন্ন ছবি, বিশেষত চার্লি চ্যাপলিন, বাস্টার কিটন, হ্যারল্ড লিয়ড এবং আর্নস্ট লুবিচের কাজের দ্বারা প্রভাবিত হবার কথাই উল্লেখ করেছেন। তাই এমনটাও হতে পারে যে ১৯৩৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘ধ্রুব’ ছবিটির বিষয়ে সত্যজিৎ জানতেনই না। যদি তাই হয় সে ক্ষেত্রে খ্যাতনামা বাঙালি কবি কাজী নজরুল ইসলাম যে সেই ছবির সহপরিচালক হবার পাশাপাশি ছবিটিতে অভিনেতা (নারদের চরিত্রে) তথা গায়কের ভূমিকাও পালন করেছিলেন সেকথা যে জনমানস স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে গেছে এটাই আরো একবার প্রমাণিত হবে। বাংলা সিনেমা জগতে নজরুলের বিবিধ অবদান। যেমন প্রথম বাঙালি মুসলিম পরিচালিত প্রযোজনা সংস্থা বেঙ্গল টাইগার পিকচার্স প্রতিষ্ঠা যেটি নজরুলের স্বাস্থ্যভঙ্গ হবার কারণে ক্রমে অবহেলিত ও শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায় সেকথা হাসান মনসুর চাতকের আলোচনা থেকে জানা যায়। দুঃখের বিষয় এটাই যে তাঁর এই প্রচেষ্টাগুলির কথা নজরুল ইনস্টিটিউট কিংবা পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধ জয়লাভ করে বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের বহু বছর পরে, ১৯৭৮-সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ দ্বারা সংরক্ষিত হয়নি। বিগত ষাট দশক ধরে ভারতবর্ষে সংঘটিত সিনেমা সংরক্ষণ প্রয়াস সত্বেও ‘ধ্রুব’ ছবিটির আঠারোটি রিলের মধ্যে মাত্র একটি দর্শকদের জন্য রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। তাই, সত্যজিৎ নজরুল পরিচালিত এই ফিল্মটির বিষয়ে অবগত হলেও, এই ফিল্মটির রিল সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষেও সম্ভবত দুঃসাধ্য ছিল। সেই কারণেই হয়ত ১৯৫৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিটিই একমাত্র সংরক্ষিত এবং সহজলভ্য বিকল্প ছিল যেটি তিনি বেছে নেন।
‘অপুর সংসার’ ছবিটির থিয়েটার দৃশ্যকে আরো অর্থবহ করে তুলতে ‘ধ্রুব’ ছবির অংশবিশেষ ব্যবহৃত হলেও এটি ফিল্ম সংরক্ষণের ধারণার সঙ্গেও সমার্থক। আদতে ১৯৯১ সালে পরিচালক জোয়েল ক্যাটজ উদ্ভাবিত সংরক্ষণতত্ত্ব শব্দটি সিনেমার পরিভাষায় যেসব পরিচালকেরা সংরক্ষিত ফিল্মের অংশবিশেষ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করেন বা নিজেদের কাজে সেগুলি ব্যবহার করেন তাঁদের কর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ফিল্ম বিশেষজ্ঞ ক্যাথেরিন রাসেল এই বিষয় নিয়ে আলোচনায় জানিয়েছেন যে এই ধরণের কাজের ক্ষেত্রে উদ্যোগী পরিচালককে প্রাথমিকভাবে অন্বেষণের কাজ চালাতে হয়। উপযুক্ত ফিল্ম খুঁজে বের করার পাশাপাশি তাঁকে যথোপযুক্ত দৃশ্যাবলীও নির্বাচন করতে হয় (অনেকটা বাস্তবিক সংরক্ষণাগারে ক্যানড ফিল্ম খোঁজার মতন) যা তাঁর কাজকে সমৃদ্ধ করবে। ছবি দেখার দৃশ্যে ‘ধ্রুব’র অংশ বিশেষ প্রদর্শনে যে ধারাবাহিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয় তার নেপথ্য কারণও এই ধরণের গবেষণা। শট রিভার্স শটের মাধ্যমে থিয়েটার দৃশ্যে ছবি দেখে মুগ্ধ দম্পতির অভিব্যক্তির দৃশ্যায়নের পাশাপাশি বড় পর্দায় ‘ধ্রুব’ দেখানোর কারণেই যে শুধু ছবিটির অংশ বিশেষ প্রদর্শিত হয়েছে তা কিন্তু নয়। আসলে, সত্যজিৎ রায় ওই পৌরাণিক ছবির এমন একটি অংশই বেছে নিয়েছিলেন যেখানে বজ্রবিদ্যুৎ সহযোগে ঝড় দৃশ্যায়িত হয়েছে। তিনি আসল ফিল্মটির ওই একই অংশের ভয় পাওয়া বন্যপ্রাণীদের ছোটাছুটির দৃশ্যটি বাদ দিয়েছেন।

১৯৩৪ সালের 'ধ্রুব' ছবির বুকলেট কভার
(অ)যথার্থ সংরক্ষণের পুনর্মূল্যায়ন
পূর্বনির্মিত ফিল্মের দৃশ্যের এই ধরণের পরীক্ষামূলক ব্যবহারের ক্ষেত্রে, ইতিপূর্বে আলোচিত সম্পাদনা রীতির প্রয়োগ ঘটানো হলে, আসল ছবিটির যথার্থ সংরক্ষণ হয়নি বলে দাবি উঠতে পারে। এরকম দৃষ্টান্ত আপেক্ষিকভাবে সংরক্ষণের প্রয়াসেরও পরিপন্থী বলেও মনে হতে পারে। তবে, রাসেল মনে করেন যে এই ধরণের পরীক্ষামূলক সম্পাদনার নেপথ্যে কোন নৈতিক প্রেরণা অবশ্যই থাকে। রাসেল একথাও বলেছেন যে এই ধরণের নৈতিক হস্তক্ষেপের ফলপ্রসূ হবার জন্য পরিচালককে খেয়াল রাখতে হবে যেন দর্শকেরা আসল ছবিটির বিষয়ে অবগত এবং তার দৃশ্যবলীর সাথে পরিচিত হন নাহলে সম্পাদনার দ্বারা যে পরিবর্তন ঘটানো হবে সেটা দর্শকের কাছে অর্থবহ হবেনা। সত্যজিৎ রায় ‘ধ্রুব’ ছবিটিকে বেছে নেওয়ার মাধ্যমে দুটি উপায়ে এই সমস্যাকে এড়াতে পেরেছিলেন। প্রথমত, ‘অপুর সংসার’ ছবিটির মাত্র ছয় বছর আগে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘ধ্রুব’ ফিল্মটির কথা সিনেমাপ্রেমী দর্শকেরা সম্ভবত ভুলে যাননি ফলে ফিল্মের ভেতর ফিল্মের তাৎপর্য অনুধাবন করতে তাঁদের সম্ভবত অসুবিধা হয়নি এবং দ্বিতীয়ত ছবিটি চিরপরিচিত একটি পৌরাণিক কাহিনী ঘিরে নির্মিত হওয়ার যাঁরা আগের ছবিটি দেখেননি তাঁদেরও বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়।
সত্যজিৎ রায় তাঁর সংরক্ষণ প্রয়াসের জন্য আসল ছবিটির এমন দৃশ্যই বেছে নিয়েছেন যেখানে কোন নারী চরিত্রকে দেখা যায় না যা তৎকালীন ছবিতে নারীদের অভিজ্ঞতাকে সদর্থকভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে উপস্থিত খামতির দিকে ইঙ্গিত করে।
দর্শকদের সহজে বোধগম্য হবার পাশাপাশি সিনেমা দেখার দৃশ্যটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে তাঁর উপন্যাসে এই দম্পতির চরিত্রায়ন করেছেন তার থেকে সরে এসে, ছবির মুখ্য নারীচরিত্র অপর্ণার প্রতি সমবেদনা জানায়। অপু এবং তাঁর স্ত্রী থিয়েটারে কোন ধরণের ছবি দেখেছিল সেই বিষয়ে বেশি কথা খরচ না করলেও, ফিল্মের গল্প ও বড় পর্দায় ছবিগুলি কিভাবে নড়াচড়া করছে সেটি ধরতে না পারার ক্ষেত্রে অপর্ণার ব্যর্থতার কথা এবং এসব বিষয় বোঝার জন্য অপুর ওপরে তার নির্ভরশীলতার কথা বিভূতিভূষণ বেশ বিস্তারিত ভাবে লিখেছেন। হতে পারে যে লেখক অপুর বুদ্ধিমত্তা এবং যুক্তিবাদী মানসিকতাকে তুলে ধরার জন্যই তাঁর লেখায় এই পরিস্থিতির অবতারণা করেন। অপরদিকে, ফিল্মে থিয়েটার দৃশ্যে যখন 'রিভার্স শট' ব্যবহার করে গল্পের দম্পতির অভিব্যক্তি প্রদর্শন করা হয় তখন দেখা যায় যে 'ধ্রুব' ছবিটি দেখে অভিভূত অপর্ণার চোখে জল কিন্তু অপুর অগম্ভীর মুখভাব বলে দেয় যে ওই ছবির গল্পের গভীরতা তাকে স্পর্শ করেনি ও তার মনে সমবেদনার সঞ্চারও করেনি। অপর্ণার ছবিটির কাহিনী কারোর সাহায্য ছাড়াই উপলব্ধি করতে পারা বিভূতিভূষণের চরিত্রায়নের সম্পূর্ণ বিপরীতে সাক্ষ্য দেয়। তাছাড়া, দর্শকেরা যখন জানতে পারেন যে অপর্ণা মা হতে চলেছে তখন ধ্রুবর কাহিনী দেখে তার আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ার ঘটনায় এক নতুন মাত্রা যোগ হয়। একটি ধর্মকেন্দ্রিক, অতিপ্রাকৃতিক ছবি দেখে যুক্তিবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ অপুর আবেগহীন মুখভাবকে দৃশ্যায়িত করলেও এক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায় উপন্যাসের বর্ণনা থেকে সরে গিয়ে যুক্তিবাদের সীমাবদ্ধতাকে যেমন ফুটিয়ে তুলেছেন তেমনই যুক্তিবাদকে তিনি অপর্ণার আচরণে প্রকট মাতৃত্ব থেকে উৎসারিত আবেগপ্রবণতার চেয়ে উচ্চাসনেও স্থান দেননি। সত্যজিৎ রায় তাঁর সংরক্ষণ প্রয়াসের জন্য আসল ছবিটির এমন দৃশ্যই বেছে নিয়েছেন যেখানে কোন নারী চরিত্রকে দেখা যায় না যা তৎকালীন ছবিতে নারীদের অভিজ্ঞতাকে সদর্থকভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে উপস্থিত খামতির দিকে ইঙ্গিত করে।
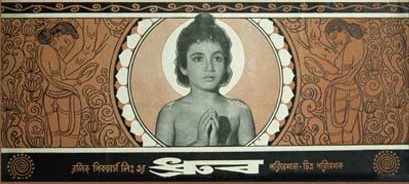
১৯৫৩ সালের 'ধ্রুব' ছবির বুকলেট কভার
‘ধ্রুব’ ছবিটির শৈল্পিক সংরক্ষণের পাশাপাশি অপুর সংসার ছবিটি তখনকার দিনে সিনেমা দেখার সাথে জড়িত বিভিন্ন অভ্যাস এবং স্মৃতিকেও ছুঁয়ে দেখে। যেমন, অপর্ণার হাতে দেখা যায় সরু, পাকানো ঠোঙা ধরা যাতে খুব সম্ভবত চিনাবাদাম ভর্তি। তখনকার দিনে সাধারণত সিনেমা হলে ঢোকবার আগে দর্শকেরা এরকমই চিনাবাদামের ঠোঙা বাইরের বিক্রেতাদের থেকে কিনে নিতেন। তাছাড়া, যেসব দর্শকেরা ‘ধ্রুব’ ছবিটি যে শ্রী, প্রাচী ও পূর্ণা এই তিনটি হলে মুক্তি পেয়েছিল সে বিষয়ে অবগত, অপুর সংসার ছবিটি দেখবার সময় তাঁদের হয়ত নিজেদের ওই ছবিটি দেখার স্মৃতি মনে পড়ে যাবে। যদিও সত্যজিৎ রায় যে উল্লেখিত সিনেমাহলগুলির একটিতেও শ্যুটিং করেছেন এই বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়, তিনি এই থিয়েটার দৃশ্যের মাধ্যমে স্মৃতিচারণকে প্রশ্রয় দিয়েছেন যা ফিল্ম সংরক্ষণের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলির একটি।
যখন এনএফএআই প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছিল তখন এটির ভূমিকা এবং কার্যকারিতা ঘিরে জল্পনাকল্পনা ও উত্তেজনা তুঙ্গে ওঠে। এই প্রতিষ্ঠানটি কী কেবলই ক্যানড ফিল্মসগুলিকে সংরক্ষণ করবে নাকি বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনের জন্য সেগুলি সরবরাহ করার দায়িত্বটিও পালন করবে? সংরক্ষণের অর্থ কী শুধুই রক্ষা করা নাকি সম্প্রচারের ব্যবস্থাও এই কাজের অঙ্গ? আসলে, সংরক্ষনাগারের সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টাই ছিল এই দ্বন্দ্বের মূলে। এহেন মতবিরোধের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সত্যজিৎ রায় ‘অপুর সংসার’ ছবিতে একটি সংরক্ষিত ছবির অংশবিশেষ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন। নতুনভাবে ওই অংশটি তৈরি করার পরিবর্তে, মিনিট খানেকের জন্য হলেও তিনি একটি পুরানো ছবির অংশবিশেষ সম্পাদনার মাধ্যমে সেটিকে নিজের ছবিতে সংরক্ষণ করেছেন বা বলা যায় তিনি নিজের ফিল্মকেই আরেকটি ফিল্মের সংরক্ষনাগারে পরিণত করেছিলেন।
লেখক পরিচিতি
স্রগ্ধরামালিনী দাস কলকাতার মেয়ে, স্বাধীন গবেষক। ২০২২ সালে চিত্রসমালোচনার জন্য পেয়েছেন চিদানন্দ দাশগুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার। মনিপাল সেন্টার অফ হিউম্যানিটিজ থেকে ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর। উনিশ এবং বিশের শতকে মেয়েদের লেখালেখি তাঁর গবেষণার বিষয়। পাশাপাশি নিয়মিত লেখেন ভারতীয় চলচ্চিত্র নিয়ে। তাঁর প্রবন্ধ এর আগে প্রকাশিত হয়েছে দ্য স্টেটসম্যান, ফিল্ম কম্প্যানিয়ন এবং ই-সিনে ইন্ডিয়ায়।