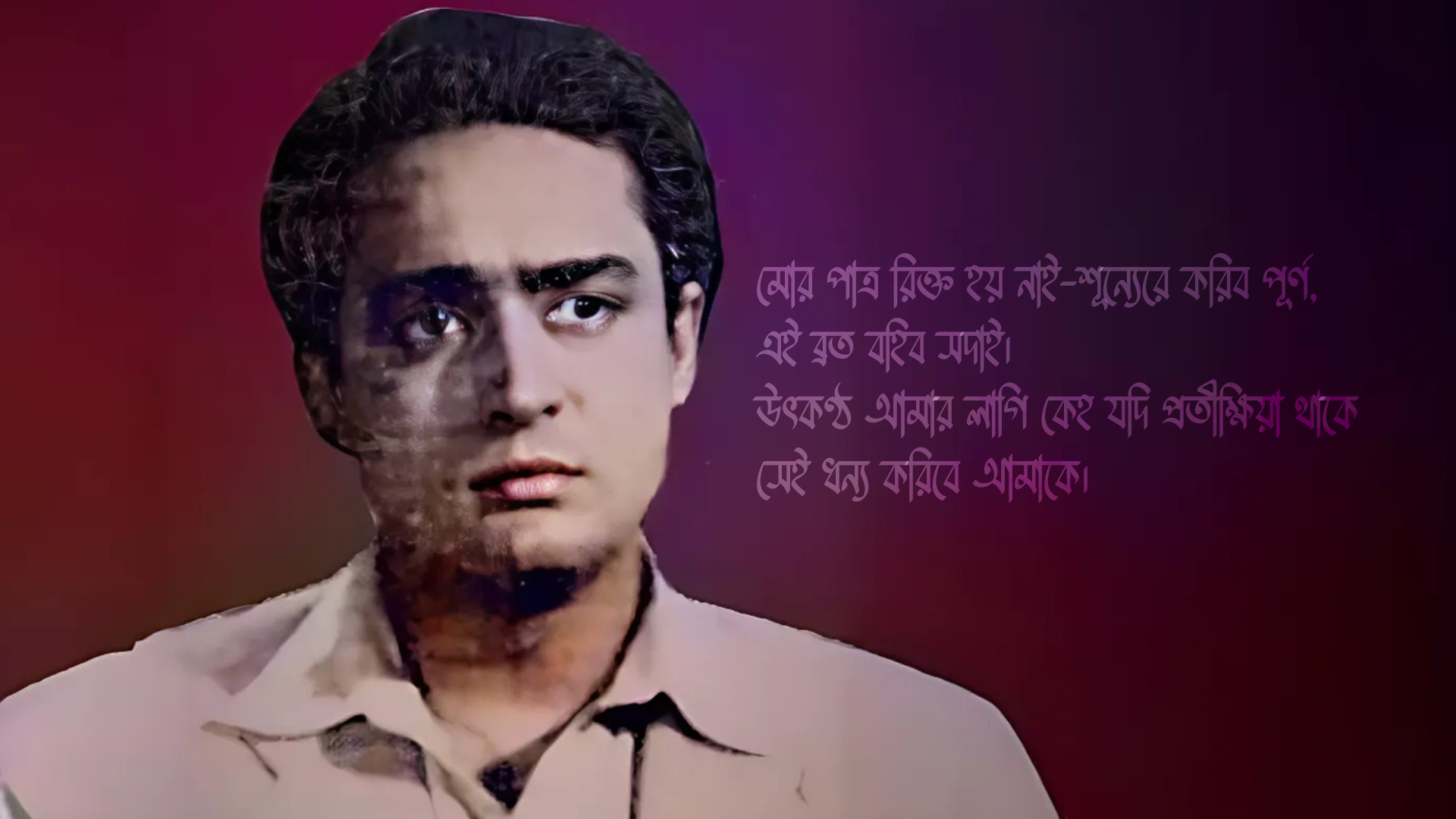
জন্মদিনে উপহারে ভরিয়ে দেওয়ার কথা তাঁকেই। কিন্তু নিজের ৯৫তম জন্মদিনের জন্য ভূমিকাটা বদলে নিলেন নির্মল কুমার। উপহার নিয়ে হাজির হলেন তিনিই। বাংলা ছবির প্রবীণতম এই অভিনেতা নাতনি উপাসনা আর নাতি অনীশের জন্য চিঠি লিখতে বসলেন। নিজের প্রথম ছবি শেষের কবিতার সেই স্মৃতি লিখনের ভাগ পেল BFA-ও।
BFA এই কাজের দায়িত্ব নিল কেন:
ফিল্মে
কাজ করাটা আমার ক্ষেত্রে ছিল পুরোপুরি কাকতালীয় বিষয়। এমনিতে অভিনয়ের প্রতি আমার অবশ্য একটা
টান ছিল। সবিতাব্রত দত্ত, সন্তোষ দত্ত আর আমি মিলে আনন্দম নামের একটি থিয়েটার
গ্ৰুপ চালাতাম। সবিতাব্রত আর আমি তখন কলকাতা হাইকোর্টে কাজ করতাম। হাইকোর্টের আরো
অনেকেই আনন্দমের অংশ হয়ে উঠেছিলেন।
একদিন
আমি যখন রাসবিহারী অ্যাভেনিউয়ের কাছে একটা চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে ব্যস্ত তখনই
সবটা বদলে গেল। সবিতাব্রত, যার ডাকনাম ঝনু, আমায়
থামিয়ে বলল, "নির্মল, তোমায়
আমার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে হবে।" কোথায় যেতে হবে জিজ্ঞেস করতে সে আমায় মধু বসুর
নাম বলল। আমি হতবাক হয়ে গেছিলাম, মধু বসু-সাধনা বসুর মতন বড়
মাপের ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা করে কি করব বুঝতে পারছিলাম না। নাছোড়বান্দা
হয়ে ঝনুকে বলি যে সাক্ষাতের কারণটা জানাতেই হবে। তখন ও আমায় বলেছিল যে মধু বসু'শেষের কবিতা' নিয়ে
কাজ করতে চান এবং অমিত রায়ের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য কাউকে খুঁজছেন। ঘটনাক্রমে, পরের সপ্তাহেই শুটিংয়ের কাজে ওনাদের শিলং যাওয়ার কথা
কিন্তু তখনও পুরুষ মুখ্যচরিত্রটির জন্য যথাযোগ্য কোন অভিনেতাকে পাওয়া যায়নি।
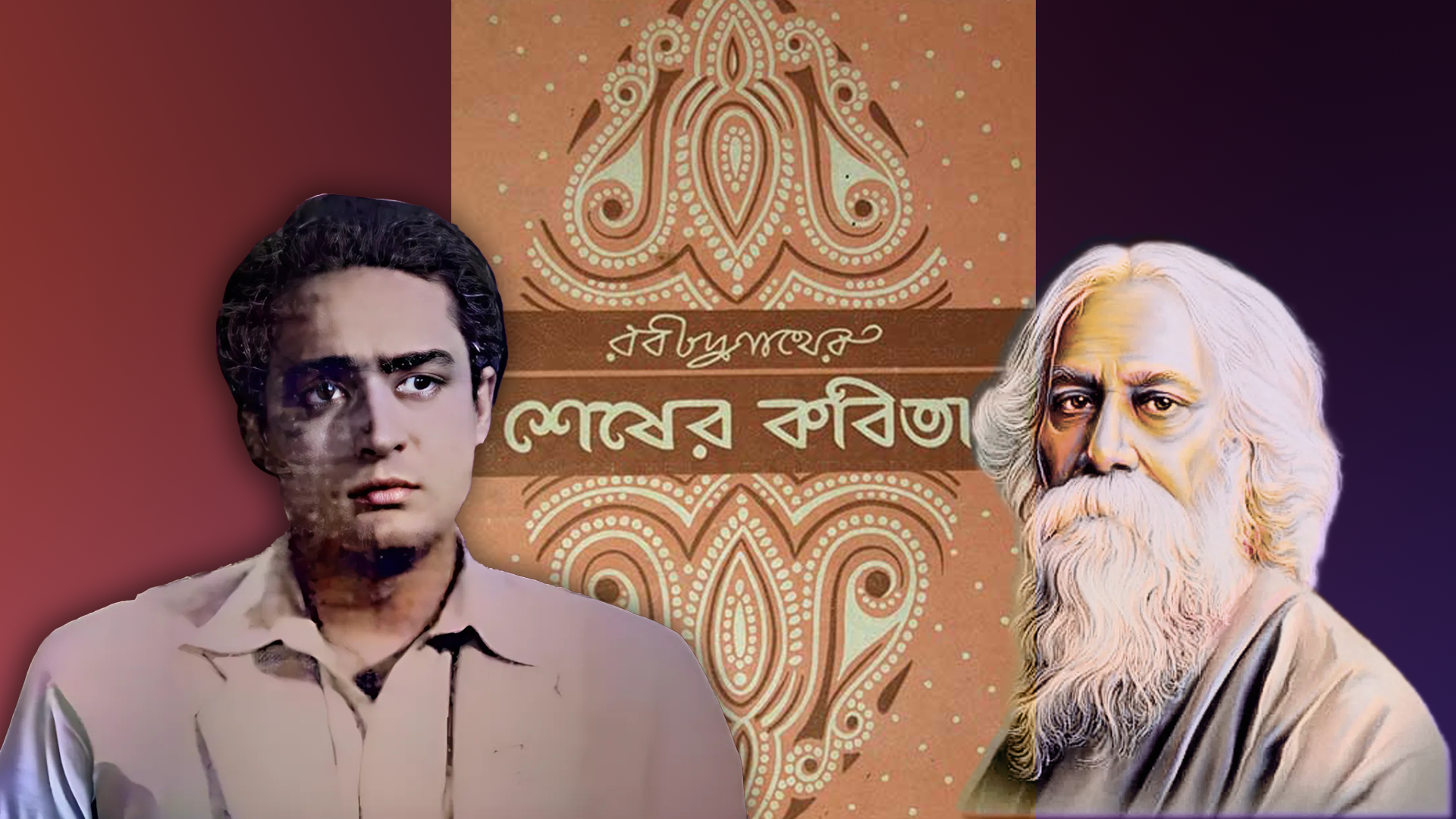
সেই
সময়ে, অসিত বরণের খুব নামডাক ছিল। উত্তম কুমার তখনও অতটা
জনপ্রিয় হননি। কিন্তু মধু বসু তাঁদের কাউকেই এই চরিত্রের জন্য যোগ্য বলে মনে
করেননি। তিনি নতুন মুখের সন্ধানে ছিলেন আর প্রোডাকশন কন্ট্রোলার মণিলালদা (মণিলাল
শ্রীবাস্তব) ভেবেই পাচ্ছিলেন না যে কী করে ঠিকঠাক কাস্টিং করা যায়। ঝনুকে ডাকা
হয়েছিল কিন্তু চরিত্রের সঙ্গে ওকে মানাচ্ছিল না। ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার পরেই মধু বসু
ওকে বলেছিলেন যে ওর চেহারায় সেই ব্যাপারটা নেই যেটা অমিত রায়ের চরিত্রে অভিনয় করতে
গেলে প্রয়োজন। অভিজ্ঞ সেই পরিচালক ঝনুকে বলেছিলেন, "আমি
তোমার সময় নষ্ট করব না। তোমার চেহারায় একটা ভালমানুষি ভাব আছে। অমিত রায় কিন্তু
একদম ওরকম নয়। সে হল ঝোড়ো হাওয়ার মতন, যে কোন
মুহূর্তে যা খুশি করে ফেলতে পারে। আমি এমন একজনকে খুঁজছি যার চলাফেরাই অন্যরকম
হবে। তাকে যে খুব ভাল অভিনেতা হতেই হবে তা নয়। অভিনয় আমি তাকে দিয়ে করিয়ে নিতে
পারব।"
কথাবার্তা
চলাকালীন ঝনু আমার নামটা ওনাকে বলেছিল। বলাবাহুল্য, নতুন
একজনের সঙ্গে আলাপ করতে উনিও উৎসুক ছিলেন। আমি যে ওর সাথেই অভিনয় করি সেটা ছিল
উপরি পাওনা। ঝনু আমায় বলে হাইকোর্টের কাজ মিটলে ওনার হোটেলে ওনার সঙ্গে দেখা করতে।
প্রথমে দেখা করা নিয়ে আমার মনেও সন্দেহ ছিল। সত্যি বলতে, আমি ঝনুকে বলেছিলাম যে আমি প্রস্তুত নই। ঝনু কিন্তু
আমার ভয়কে উড়িয়ে দিয়েছিল আর আমার সাথেও গেছিল।
প্রথমে, ঝনু ভেতরে গেছিল আর আমি বাইরেই অপেক্ষা করছিলাম। মধু বসু
ঝনুকে অভ্যর্থনা জানিয়েই আমার খোঁজ করেছিলেন। আমি বাইরে অপেক্ষা করছি শুনে উনি
ঝনুকে বলেন আমায় তাড়াতাড়ি ভেতরে নিয়ে আসতে। পরিচয় পর্বের পরে উনি আমার বলেন যে উনি
জানেন আমি ঝনুর সঙ্গে নাটকে অভিনয় করি। উনি এটাও বলেন যে উনি একটি নাটক দেখেছেন আর
একটা ছোট চরিত্রে আমার অভিনয় ওনার ভাল লেগেছিল। এর পরে উনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন
ওনার আমায় ডেকে পাঠানোর কারণ আমি জানি কিনা। আমি বললাম। এর পরে উনি আমায় বললেন যে
উনি চান আমি অমিত রায়ের ভূমিকায় অভিনয় করি এবং জিজ্ঞেস করলেন আমি 'শেষের কবিতা' পড়েছি
কিনা।
উত্তম কুমার তখনও অতটা জনপ্রিয় হননি। কিন্তু মধু বসু তাঁদের কাউকেই এই চরিত্রের জন্য যোগ্য বলে মনে করেননি। তিনি নতুন মুখের সন্ধানে ছিলেন আর প্রোডাকশন কন্ট্রোলার মণিলালদা (মণিলাল শ্রীবাস্তব) ভেবেই পাচ্ছিলেন না যে কী করে ঠিকঠাক কাস্টিং করা যায়।
আমার
সাহসটা ভাব, উনি যেই জিজ্ঞেস করলেন আমি অমিত রায়ের চরিত্রে অভিনয়
করতে পারব কিনা আমি তৎক্ষণাৎ হ্যাঁ বলে দিলাম। আমি বলেছিলাম, "অমিত রায়ের চরিত্রে অভিনয় না করার কী আছে? হ্যাঁ আমি
পারব"। আমার আত্মবিশ্বাস দেখে মধু বসুও অবাক হয়ে গেছিলেন এবং ঝনুকে বলেছিলেন যে এর আগে যাকেই এই প্রস্তাব
দেওয়া হয়েছে, সে এই প্রস্তাবটি নিয়ে ভেবে দেখার সময় চেয়েছিল। আর
এখন এমন একজনকে পেলেন যে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। উনি এর পরে আমায় জিজ্ঞেস করলেন
আমায় কোন বই দিলে আমি পাঠ করতে রাজি কি না। উনি আমায় রবীন্দ্র রচনাবলী থেকে একটি
অংশ দিলেন এবং জোরে জোরে পাঠ করতে বললেন।
আমি পাঠ
করলাম এবং উনি আমায় মাঝপথে থামিয়ে দিলেন। তার পরে, আমায়
বললেন যে উনি ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে আমার ফটো তোলাতে চান। আমিও বেশ উৎসাহিত
বোধ করছিলাম তাই ওনার সঙ্গে সন্ধ্যেবেলা দেখা করতে রাজি হয়ে গেলাম। উনি আমায়
স্টুডিওতে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পৌঁছে সেখানে বসুবাবুর সহকারী
মন্টুদা'কে দেখতে পেলাম। আমায় লনে বসতে বলা হল। এর ঠিক পরেই
মধু বসু গাড়ি চালিয়ে ঢুকলেন।
"মন্টু, নতুন ছেলেটা কী এসেছে?" উনি
জিজ্ঞেস করলেন।
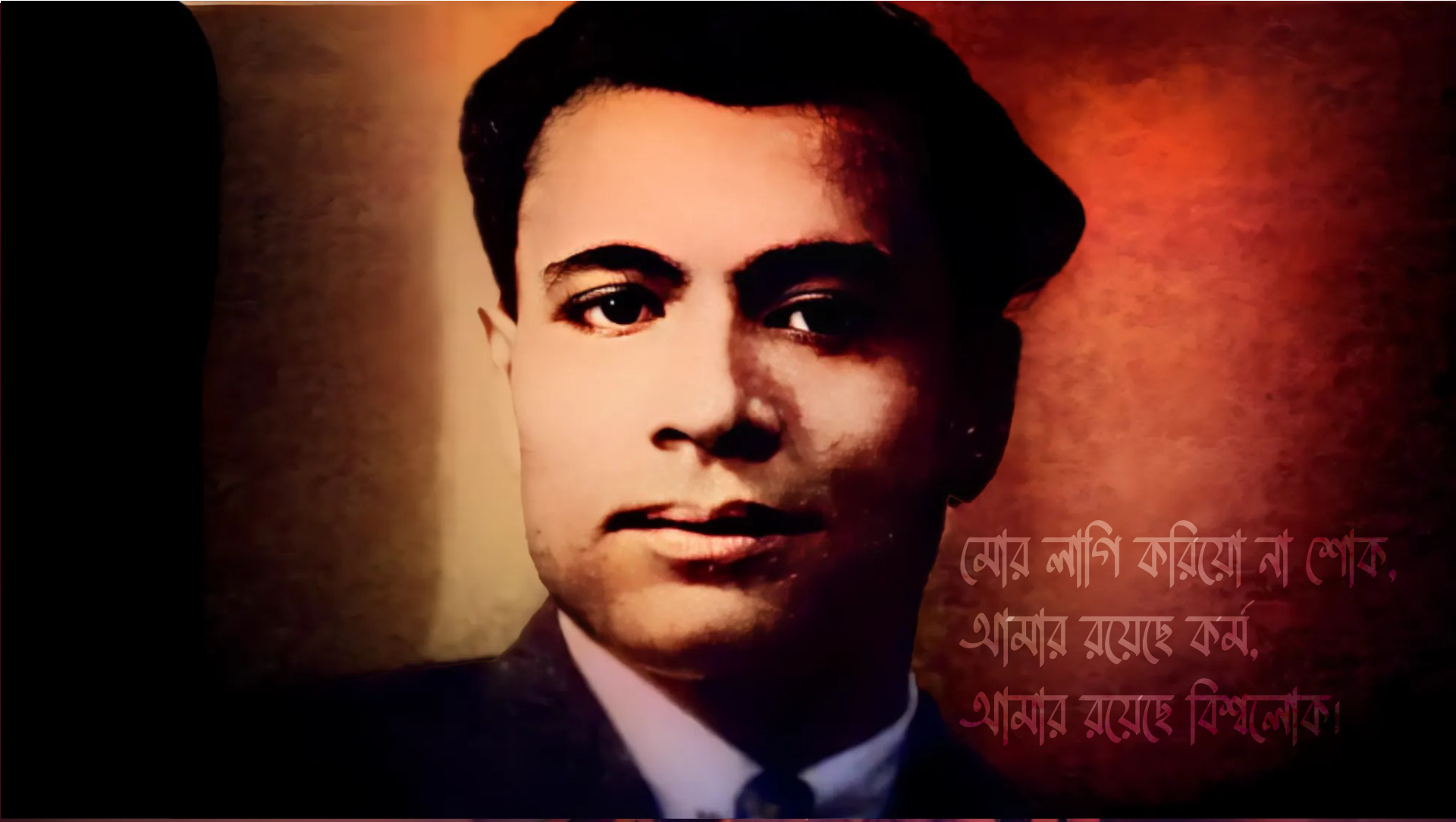
ক্যামেরাম্যান
জিকে মেহতা ফ্লোরে চলে এসেছিলেন। ততক্ষণে, অভিনেত্রী
দীপ্তি রায়ও পৌঁছে গিয়েছেন। ওনার মেকআপ করাও হয়ে গেছিল। উনি আমার দিকে দেখে বললেন, "এনার বয়স তো খুবই কম।" বসু সাহেব আমার দিকে
তাকিয়ে দেখে বললেন, "হ্যাঁ, আমি বয়স
কম এমন একজনের সাথেই কাজ করতে চাই।"
ক্যামেরাম্যান
আমাদের একক ছবি তুললেন। দীপ্তি রায় এবং আমার একসাথেও ছবি তোলা হল। বসু সাহেব দেখতে
চেয়েছিলেন আমাদের একসঙ্গে কেমন মানায়। উনি আমায় বললেন, "তোমার কণ্ঠস্বর বা সংলাপ পাঠ এগুলো নিয়ে আমার তেমন
চিন্তা নেই। আমার চিন্তা হল তুমি ক্যামেরার সামনে কতটা ভালভাবে কাজটা করতে পারব।"
আমি
বাচ্চাদের মতন বলে উঠলাম আমি তো ক্যামেরার সামনে নির্ভয়ে নৃত্য করব। উনি বলে উঠলেন, "কী? তুমি নাচবে?" তক্ষুণি
নিজেকে শুধরে নিয়ে বললাম: "চিন্তা করবেন না। ক্যামেরার সামনে আমি স্বচ্ছন্দে
অভিনয় করতে পারব।"
একটু
নিশ্চিন্ত হয়ে উনি বললেন, "দেখা যাক কেমন কাজ তুমি কর। তোমার কাছে গরম জামা আছে
তো? আমি আমার প্রোডাকশনের লোকেদের বলে দেব তোমায় নিয়ে
গিয়ে প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্র কিনে দিতে যেগুলো শিলংয়ে থাকাকালীন কাজে লাগবে। ওরাই
টাকাপয়সা মিটিয়ে দেবে, তোমায় দাম দিতে হবে না।"
ততক্ষণে, অভিনেত্রী দীপ্তি রায়ও পৌঁছে গিয়েছেন। ওনার মেকআপ করাও হয়ে গেছিল। উনি আমার দিকে দেখে বললেন, "এনার বয়স তো খুবই কম।" বসু সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে দেখে বললেন, "হ্যাঁ, আমি বয়স কম এমন একজনের সাথেই কাজ করতে চাই।" ক্যামেরাম্যান আমাদের একক ছবি তুললেন। দীপ্তি রায় এবং আমার একসাথেও ছবি তোলা হল।
গোটা
ইউনিটে আমার একজন মাত্র পরিচিত অভিনেতা ছিল। সে হল উৎপল (উৎপল দত্ত)। আমি ইন্ডিয়ান
পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশনে (আইপিটিএ) কাজ করেছিলাম। উৎপল সেই সময়েই আইপিটিএ-তে
যোগ দিয়েছিল। বসুসাহেব উৎপলকে মাইকেল মধুসূদনের ভূমিকায় অভিনয় করিয়েছিলেন। তিনি
উৎপলের অভিনয়ের রীতি এবং তার বাংলা ও ইংরাজিতে সমান দক্ষতার সঙ্গে কথা বলার
ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করতেন। তিনি আমায় বলেছিলেন, "উৎপলও
শিলংয়ে যাবে। ওর জন্যেও আমি একটা ছোট চরিত্র রেখেছি।"
মণিলালদা'র ওপরে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল নিউমার্কেটের কাছে একটা
বড় দোকান থেকে শীতবস্ত্র কেনার। কয়েক দিনের মধ্যেই আমায় বলা হল যে আমরা গুয়াহাটি
যাব বিমানে আর সেখান থেকে গাড়িতে শিলংয়ে যাওয়া হবে। ওটাই ছিল আমার প্রথম বিমান
সফর। সেটা ছিল একটা ডাকোটা প্লেন যেটা ওড়ার সময় প্রচন্ড শব্দ করছিল। আমায় বলা
হয়েছিল বিমানে থাকাকালীন ইয়ার বাড ব্যবহার করতে যাতে ওই অসহনীয় শব্দে কোন শারীরিক
সমস্যা না হয়। আমি মজা করে বলেছিলাম, নাকেও একটু তুলো গুঁজে দেব কিনা!
পাহাড়ি
পথ ধরে গাড়িতে শিলং যাওয়াটা ছিল মনে রাখার মতন। এমন সুন্দর ছবির মতন জায়গা আগে আমি
দেখিনি। বসু সাহেব মাঝপথে গাড়ি থামিয়ে ছিলেন আর বলেছিলেন পাহাড়ের ঠিক গায়ে দোতলা
এক হোটেলে চা পানের জন্য একটু দাঁড়াতে হবে। সন্ধ্যের মধ্যে আমরা শিলংয়ে পৌঁছে
গেছিলাম।
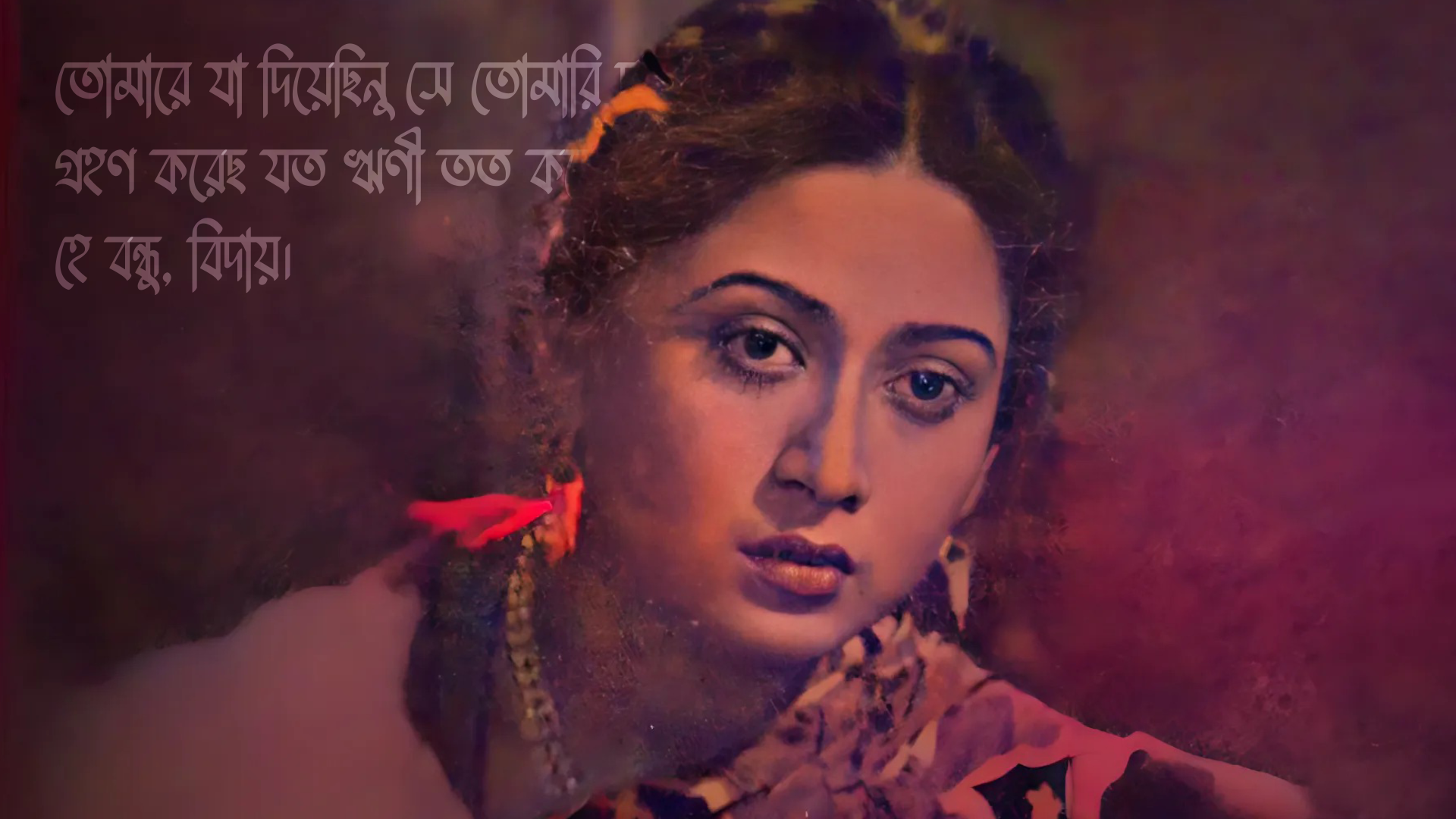
ইউনিটের
থাকার জন্য দুটো হোটেল বুক করা হয়েছিল। উৎপল আর আমি একটা হোটেলের দুটো ঘরে ছিলাম। বসু
সাহেবের সবচেয়ে প্রিয় অভিনেতা টুকলুদা'ও ওখানে
ছিলেন। দীপ্তি রায়ের অন্য হোটেলে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। রাতে আমি যখন বসু সাহেবের
সঙ্গে তাঁর হোটেলে দেখা করতে যাই, উনি মন্টুদা'কে শ্যুটিংয়ের প্রথম দিনে আমায় কী করতে হবে সেটা
বুঝিয়ে দিতে বলেন।
সত্যি বলতে, কাজটা এমন কিছু শক্ত ছিল না। আমার প্রথম দৃশ্যে আমার কাজ ছিল আমার হোটেলের সামনে পায়চারি করা। আরেকটা দৃশ্য ছিল যেখানে আমি টুকলুদা'কে বলব, "এই, এই শুনছেন?" বসু সাহেব আমায় এটা তিন চারবার বলতে বলেন। শেষ পর্যন্ত আমি সিনেমাটোগ্রাফারকে জিজ্ঞেস করি আমি ঠিকঠাক করতে পারলাম কিনা। তিনি আমায় চিন্তা করতে বারণ করলেন আর বললেন যে পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হলে বসু সাহেব আবারও রিটেক করতে বলতেন।
উনি বলেছিলেন, "অমিত রায় পুরো সাহেব, তার উচ্চারণ বাঙালি ঘেঁষা হলে সেটা হবে মোক্ষম এক ভুল। উচ্চারণটা হবে 'দাআর-জিলিং', 'দার্জিলিং' নয়।" কত বার যে আমি ব্রিটিশদের মতন 'দাআর-জিলিং' বলা রপ্ত করেছিলাম তা আর গুনতে পারিনি।
সেই
রাতেই ক্যানড শটসগুলি বিমানযোগে কলকাতায় পাঠানো হয় ও ল্যাবরেটরিতে প্রিন্ট করানো
হয়। শিলংয়ে বসুসা হেবকে প্রিন্ট দেখানো হয়। পরের দিন আমরা শুনলাম যে প্রিন্ট এসে গেছে। উনি আমায় বললেন, "নির্মল তুমিও এসো আমার সঙ্গে, দেখবে তুমি কেমন কাজ করেছ।" সেই প্রথমবার আমার
একটু চিন্তা হচ্ছিল। আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি
চান আমি সঙ্গে যাই?" উনি বললেন,"অবশ্যই তোমায়
তো যেতেই হবে। এটা তো তোমার ফিল্ম। তোমায় দেখতে হবে তুমি কেমন অভিনয় করলে আর কোথায়
ভুলচুক হয়েছে।" আমার কিন্তু ফলাফল দেখে বেশ ভালোই লাগল। বসু সাহেব উৎপলকে তার
অভিমত জিজ্ঞেস করলেন। উৎপল বলল, "ঠিকই আছে।"
পরের দিন
আবার আমাদের শ্যুটিং ছিল। আমায় একটি চিত্রনাট্য দেওয়া হল। উনি বললেন, "এখন খবরের কাগজখানা পড়ো না, ভোর থাকতে চিত্রনাট্যে মন দাও। যদি কোন অসুবিধা থাকে
আমাকে বা আমার সহকারীকে জিজ্ঞেস করে নিও।" আমার কোথাও সমস্যা হলেই ওনার কাছে
সাহায্য চাইতাম। একবার উনি আমাকে একটা লাইন নানা রকম ভাবে বলতে বলেছিলেন। উনি
বলেছিলেন, "আমার যে বলার ধরণটা পছন্দ হবে সেটাই বেছে নেব।"
অমিত
রায়ের চরিত্রের জন্য ইংরাজি উচ্চারণ হতে হত একদম যথাযথ। আমি 'দার্জিলিং' শব্দটা
খানিকটা বাঙালি ধাঁচে উচ্চারণ করছিলাম। বসু সাহেবের স্বাভাবিক ভাবেই সেটা পছন্দ
হয়নি। উনি বলেছিলেন, "অমিত রায় পুরো সাহেব, তার
উচ্চারণ বাঙালি ঘেঁষা হলে সেটা হবে মোক্ষম এক ভুল। উচ্চারণটা হবে 'দাআর-জিলিং', 'দার্জিলিং' নয়।" কত বার যে আমি ব্রিটিশদের মতন 'দাআর-জিলিং' বলা
রপ্ত করেছিলাম তা আর গুনতে পারিনি।
জন
ডানের একটি কবিতা আমায় আবৃত্তি করতে হত। বসু সাহেব আমায় শিখিয়েছিলেন কিভাবে ওই
লাইনগুলো বলতে হবে। উনি পরিমিতিতে বিশ্বাসী ছিলেন তাই মাত্র পাঁচ-ছয় লাইনই আবৃত্তি
করতে বলেছিলেন। আমার নির্ভীক মানসিকতা এক্ষেত্রে আমায় খুব সাহায্য করেছিল।

উৎপলও
আমায় খুব সাহায্য করেছিল। আমি যখন ওকে জিজ্ঞেস করতাম ঠিক হচ্ছে কিনা, ও বলত: "ঠিক আছে। যা করছিস, এটাই করবি। বসু সাহেব তো তোকে দেখিয়ে দিয়েছে...সে ভাবে
করে যাবি। তার পর ওরা দেখে নেবে।"
উৎপল
তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছিল। ওর খুব বেশি দৃশ্যে কাজ ছিলনা। বেশির ভাগ দৃশ্যই ছিল আমার
এবং দীপ্তি রায়ের মধ্যে। আমরা ওখানে সপ্তাহখানেক ছিলাম। কলকাতায় ফিরে আসার পরে
ল্যাবরেটরিতে আমরা পুরো ফিল্মটা দেখেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল যে বেশ কিছু দৃশ্যে
আমি আরো ভাল অভিনয় করতে পারতাম। চলাফেরার ধরণটা ঠিক ছিল না। বসু সাহেব আবার আমায়
মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে অমিত রায় পুরো ব্রিটিশদের মতন। তাই তার চলাফেরায় সাবলীলতা
থাকা প্রয়োজন। উনি আলাদা করে অন্দরে আমার চলাফেরার শট নিতে চাইলেন। সেটা কেমন ভাবে
করব তা আমায় অভ্যাস করতে হয়েছিল। ওই সাবলীলতা আনতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।
বসুসা হেব
খুবই খুঁতখুঁতে স্বভাবের ছিলেন। তাই জন্যই উৎপল মাইকেল মধুসূদনের ভূমিকা নিখুঁত ভাবে
ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিল। উৎপল কিন্তু আগেই বসু সাহেবের নিখুঁত কাজের প্রতি আসক্তির
কথা আমায় জানিয়েছিল। ওনার সঙ্গে কাজ করতে গেলে যেমন তেমন করে করলে চলবে না। ওনার
যদি কিছু পছন্দ না হয় তা হলে সেই দৃশ্য উনি রাখতেন না।
আমার মনে হয়েছিল যে বেশ কিছু দৃশ্যে আমি আরো ভাল অভিনয় করতে পারতাম। চলাফেরার ধরণটা ঠিক ছিল না। বসুসাহেব আবার আমায় মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে অমিত রায় পুরো ব্রিটিশদের মতন। তাই তার চলাফেরায় সাবলীলতা থাকা প্রয়োজন।
যখন
শ্যুটিং চলছিল সেই সময় দীপ্তি রায় ছিলেন আমার চেয়ে কিছুটা বড়। সাধনা বসু, যিনি কেটি (মিটার)-এর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, তিনি আমার চেয়ে বয়সে অনেকটাই বড় ছিলেন। বসু সাহেব তাই
সাধনা বসু এবং আমার একসঙ্গে কোন দৃশ্যের চিত্রায়ণ করেননি। তার পরিবর্তে উনি আমাদের
আলাদা করে ক্লোজ-আপ নিয়ে নিতেন।
বসু সাহেবই
এই ব্যাপারটায় জোর দিয়েছিলেন যে আমি যেহেতু ফিল্মের নায়ক তাই এর প্রত্যেকটি বিষয়ই
আমার জানা উচিত। উনি আমায় বলেন যে আমায় জানতেই হবে কেমন করে আলো ব্যবহার করতে হয়।
আমাদের সিনেমাটোগ্রাফার ছিলেন খুবই অভিজ্ঞ। উনি আমায় আলো কেমন ভাবে কাজ করে সেটা
বুঝতে সাহায্য করেছিলেন। যদি কোন দৃশ্য এক সপ্তাহ ধরে শ্যুট করা হত তাহলে বসু সাহেব
সেটাকে তক্ষুণি প্রিন্ট করে খুঁটিয়ে দেখতেন। ভাল না লাগলে উনি সেই দৃশ্য আবার
তুলতেন।
১৯৫৩ সালের, ৪ঠা ডিসেম্বর, লাইটহাউসে
ফিল্মটি মুক্তি পায়। বসু সাহেব কলকাতার সব নামিদামি মানুষদের স্ক্রিনিংয়ে
ডেকেছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন উদয় শঙ্কর এবং অমলা শঙ্করের মতো অনেক খ্যাতনামা
ব্যক্তিত্ব। আমি বেশ চিন্তায় ছিলাম। মধু থিয়েটারের থেকে হাঁটা দূরত্বের একটি
হোটেলে থাকছিলেন। কিন্তু উনিও এতটাই উদ্বিগ্ন ছিলেন যে স্ক্রিনিংয়ে জন্য আসেননি।
আমিও
দুশ্চিন্তায় ভুগছিলাম এবং শেষ সারিতে চুপ করে বসেছিলাম। বসু সাহেব আমায় ফিল্মটা
দেখতে বলেছিলেন আর তার পরে ওনার সঙ্গে হোটেলে গিয়ে দেখা করতে বলেছিলেন। স্ক্রিনিং
শেষ হতেই সবাই চাইল ছবির অমিত রায়ের সঙ্গে সামনাসামনি সাক্ষাৎ করতে। ভাগ্যচক্রে আমি ততক্ষণে নীচে নেমে এসেছিলাম এবং বসু সাহেবের সঙ্গে
দেখা করতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। কিন্তু স্ক্রিনিংয়ে যাঁরা ছিলেন তাঁরা
তো সে সব শুনতে নারাজ। আমার প্রথম কাজের সকলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। আমি ভাবতেই
পারিনি যে ফিল্মটি এত মনোগ্রাহী হবে। আমি এতটাই ভয় পেয়েছিলাম যে স্ক্রিনিংয়ের সময়
ফিল্মটা কতটা ভাল হয়েছে সেটা বুঝতেও পারিনি।
সবার
প্রশংসা ধ্বনির মাঝেই আমি রওনা হলাম বসু সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। উনি আমার মতামত
জানতে চাইলেন। আমি বলে বসলাম যে আমার অভিনয় আরো ভাল হতে পারত। ওনার
উত্তর ছিল, "সে তো হবারই কথা। কিন্তু সে সব দেখে নেওয়া যাবে। গোটা
ফিল্মটা দেখে তোমার কী মনে হল?" আমি বললাম সবাই আমায়
অভিনন্দন জানিয়েছে। উনি আমার কথা শুনে তার পর বললেন, "এ বারে
দেখা যাক দর্শকদের কেমন লাগে।"

সেই
সময়ের কথা ভাবলে মনে হয় মধু বোসের মতন এমন মনোযোগী এবং যত্নবান পরিচালক খুঁজে
পাওয়াই দুষ্কর। উনি কোন অসম্পূর্ণ কাজকেই অনুমোদন দিতেন না। সব কিছুই আমাদের
দেখিয়ে দিতেন। যে কোন দৃশ্যের বিষয়ে আমার অভিমত জানতে চাইতেন। উনি ভরসা রাখতেন যে
কোন দৃশ্য ঠিক না হলে আমি সেই বিষয়ে নিজের মতামত ওনাকে জানাব। উনি মনে করতেন এর
ফলে আমার সঙ্গে রিহার্সাল করার পরে দৃশ্যটি আরেকবার রিটেক করতে পারবেন। শুধু নিজের
সন্তুষ্টি নিয়ে ভাবতেন তা কিন্তু নয়, উনি
অভিনেতাদের দৃষ্টিভঙ্গিকেও গুরুত্ব দিতেন। তারা যদি মনে করত কোথাও খামতি থেকে গেছে
তাহলে সেক্ষেত্রে কাঙ্খিত উচ্চতায় দৃশ্যটিকে নিয়ে যেতে আরো চেষ্টা করতেও উনি
দ্বিধা করতেন না। এই কারণেই উৎপলের মাইকেল মধুসূদন এক নজিরবিহীন উচ্চতায় পৌঁছতে
পেরেছিল।
ওনার পরিচালনার একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছিল। উনি রিহার্সালের সময় কী করতে হবে দেখিয়ে দিতেন। এমনকি কেমন ভাবে সংলাপ পাঠ করতে হবে সেটাও উনি বলে দিতেন। কিন্তু শট চলাকালীন উনি অভিনেতাদের থামাতেন না। শেষ হলে তারপর বলতেন, "এবার আমি বলি? আমার মনে হয় এই জায়গায় ডায়লগটা ঠিক বলা হল না। তুমি আবার ভাব। আরেকবার বল।" ওনার কথামতো চলার পরে আমিও বুঝতে পারতাম যে কোন জায়গায় বদল আনতে হবে সেটা উনি ঠিকই ধরেছেন। উনি বলেছিলেন, "অমিত রায় হল একটা অন্য রকমের চরিত্র, বাংলা সিনেমায় যেমনটা দেখা যায় তেমনটা নয়। তাই সেই চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে তোমায় সব দিকে কড়া নজর রাখতে হবে।" আমি সেই চেষ্টাই করেছিলাম।

